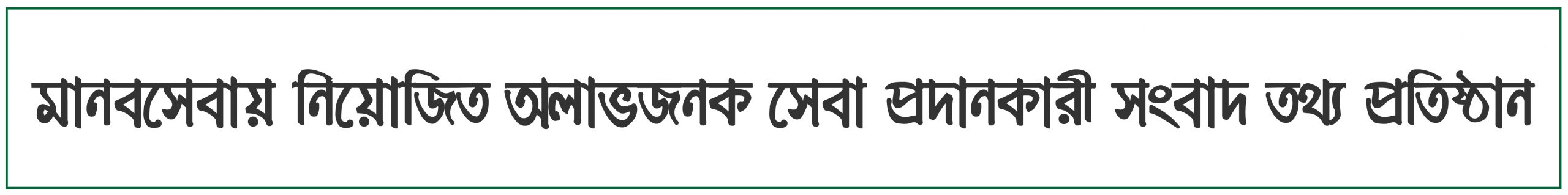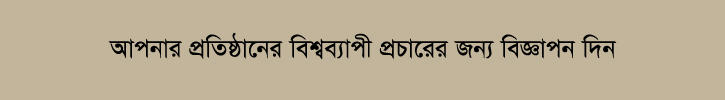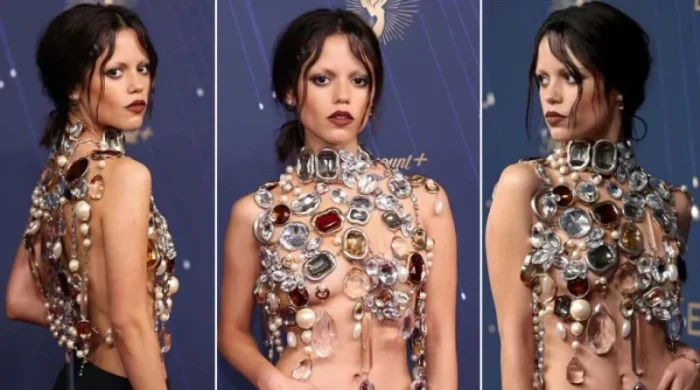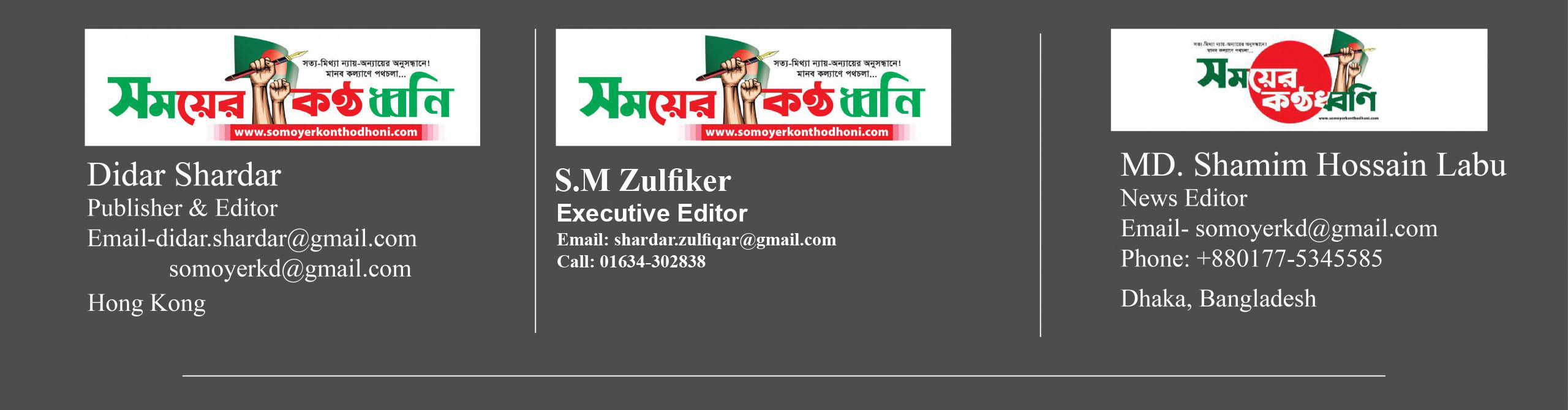হঠাৎ কেন এই যুগপৎ আন্দোলন, জামায়াতের সঙ্গে যাবে এনসিপি?
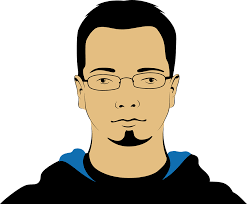
- আপডেট টাইম : সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
- ২ বার পঠিত

বাংলাদেশসহ আশপাশের দেশগুলোয় নাটকীয়ভাবে রাজনীতির মোড় বদল ঘটছে। এ রকম পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে যুক্ত করে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিকে পাঠ করা জরুরি। বিশেষ করে উচ্চতর বিদ্যাপীঠে শিক্ষার্থীদের ইউনিয়নগুলোর নির্বাচন এবং তার মধ্যেই রাজনীতির মূল ময়দানে জামায়াত-এনসিপি-খেলাফত-ইসলামী আন্দোলনসহ আটটি দলের যুগপৎ আন্দোলনের সংবাদ এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই খবরকে সংশ্লিষ্ট একাধিক দলের ‘ভিত্তিহীন’ দাবি নিঃসন্দেহে দেশ-বিদেশে রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মনোযোগ পেয়েছে।
প্রশ্ন উঠেছে, কেন হঠাৎ এই যুগপৎ আন্দোলন? এই আন্দোলনের লাভ-ক্ষতি কী? এ নিয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে দোটানাই-বা কেন?
- জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে বিএনপি যেসব বিষয়ে বিরোধিতা করছে, যুগপতের সংবাদে নাম আসা ‘আটটি দল’ সেগুলোই দাবি আকারে আনছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।
- জামায়াত আগে অন্যের নেতৃত্বে ‘যুগপৎ’ আন্দোলন করেছে বা জোটবদ্ধ থেকেছে। এবার নিজেই উদ্যোগ নিয়ে বড় ধরনের রাজনৈতিক সামর্থ্য দেখাতে চাইতে পারে।
আন্দোলন কার বিরুদ্ধে
বাংলাদেশের যুগপৎ আন্দোলনের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে সফল এক যুগপৎ আন্দোলনের ইতিহাস আছে এ দেশে। ক্ষমতাচ্যুত বিগত সরকারের বিরুদ্ধেও নানান ধরনের যুগপৎ সভা-সমাবেশ দেখেছি আমরা। তবে সেসব আন্দোলনের লক্ষ্য, প্রতিপক্ষ ও কর্মসূচির যে ধরন, তার তুলনায় সংবাদপত্রে আসা ‘আট দলের যুগপৎ আন্দোলন’-এর ধরনে অনেক ভিন্নতা থাকবে মনে হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমের প্রাথমিক প্রতিবেদনগুলোয় তাৎক্ষণিকভাবে তা-ই মনে হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য ও মূল্যায়নের জন্য আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে।
শুরুতে এ রকম যুগপৎ আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসেবে আটটি দলের নাম এলেও পরবর্তী সংবাদে দেখা গেল, ওই ‘আট’ভুক্ত কিছু কিছু দলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতা ও ভিন্নমত আছে। কোনো কোনো দলের নেতারা এ রকম সংবাদকে ‘বিভ্রান্তিকর’ও বলেছেন। এ লেখা তৈরির সময় পর্যন্ত জামায়াত যুগপৎ আন্দোলনবিষয়ক সংবাদের সত্যাসত্য বিষয়ে কিছু বলেনি।
আশির দশকে ‘যুগপৎ’ শক্তিগুলোর প্রতিপক্ষ ছিল সামরিক জান্তা সরকার। বিগত দশকে ছিল নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংসকারী সরকার। উভয় আন্দোলনের পেছনে সমাজের বড় অংশের সাধারণ সমর্থন ছিল। উপরিউক্ত উভয় ‘যুগপৎ’ নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছিল শেষমেশ। প্রশ্ন উঠতে পারে, এবারকার প্রস্তাবিত যুগপৎ শক্তির প্রতিপক্ষ কে? অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কি?
যে সরকার ‘অন্তর্বর্তীকালীন’ এবং যারা চার থেকে পাঁচ মাস পর নির্বাচন দিয়ে চলে যেতে চায় বলে জানাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার অবকাশ সামান্যই। তারপরও সম্ভাব্য ‘যুগপৎ’-এ নামার ঘোষণাদানকারী আটটি দলের কিছু দাবি সরকারের কাছেও থাকবে বলে জানা যাচ্ছে।
প্রাথমিক সংবাদের পরপরই সম্ভাব্য যুগপৎ আন্দোলনের শক্তিগুলোর পারস্পরিক বোঝাপড়া ও অঙ্গীকার নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, তবে ১৩ সেপ্টেম্বর দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তাদের দাবির ধরন ও দাবি বাস্তবায়নের পথ ও প্রস্তাব স্পষ্ট জানাচ্ছে, প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা কেবল সরকারকে নয়, বিবেচনা করছে বিএনপি ও অন্যা মধ্যপন্থী শক্তিগুলোকেও। তাদের সম্ভাব্য ‘চার দফা’র প্রথম ও প্রধান দফা হলো সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন।
এই দাবি পূরণ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, এই সরকারের সে ধরনের একক সামর্থ্য বা এখতিয়ার নেই, বরং বিএনপি চাইলে হতে পারে। আবার এমন অনেক রাজনৈতিক দল রয়েছে, যারা ২০২৪ সালের আন্দোলনে শরিক থাকলেও সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনপদ্ধতি চায় না। সুতরাং এটা বিএনপির একার ছাড় দেওয়ার ব্যাপারও নয়।
তবে ঐকমত্য কমিশনে বিএনপি যেসব বিষয়ে বিরোধিতা করছে, যুগপতের সংবাদে নাম আসা ‘আট দল’ সেগুলোই দাবি আকারে আনছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। সুতরাং এটা বলা যায়, ‘আট দল’-এর আন্দোলনের অভিমুখ বিএনপি ও একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী দলগুলোকে লক্ষ্য করে। নিশ্চিতভাবে এর অনিবার্য একটি পার্শ্বফল হবে ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর মাঝে আনুষ্ঠানিক ভাঙন ও বৈরিতা শুরু হওয়া।
প্রস্তাবিত ধাঁচে কথিত যুগপৎ আন্দোলন শুরু হলে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এত দিন যে বিরুদ্ধতা মৌখিক তর্কবিতর্কে দেখা যেত, সেটা পূর্ণ রাজনৈতিক চেহারা নেবে বলে অনুমান করা যায়। হয়তো তাতে সমাজে বাড়তি উত্তাপ ও উত্তেজনাও ছড়াবে। নিশ্চিতভাবে এটা ২০২৪ সালে ক্ষমতাচ্যুত শক্তির জন্য একটা ‘বিজয়’ হবে।
তাদের ‘প্রতিপক্ষ’গুলো আর একসঙ্গে নেই এবং বহুদিনের জন্যই সেসব ‘প্রতিপক্ষে’র মধ্যে বৈরিতার বীজ রোপিত হচ্ছে—এটা বিগত দিনের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও তাদের মিত্রদের জন্য উদ্যাপন করার মতো উপলক্ষ বটে। ১৩ থেকে ১৪ মাসের ভেতর তাদের এই প্রাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। তবে এটা নেতিবাচক এক প্রাপ্তি হবে। এটা তাদের জন্য আরাম বোধ করার মতো বিষয় হলেও এতে তাদের কোনো রাজনীতি দাঁড়াবে না। তার অতীতও মুছে যাবে না।
সে তুলনায় ‘আটটি দলের যুগপৎ আন্দোলন’-এর উদ্যোগে লাভ হবে জামায়াতে ইসলামীর। আরও সরাসরি বললে, সত্যি সত্যি এই যুগপৎ আন্দোলন শুরু হলে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে জামায়াতের সামগ্রিক অর্জন তার গত পাঁচ দশকের যাবতীয় সফলতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।
সম্ভাব্য যুগপৎ আন্দোলন ও তার লাভ-ক্ষতি
ডাকসু নির্বাচনে জামায়াতের ছাত্রশক্তির বিজয় তাদের জাতীয় ক্ষমতার মূল যুদ্ধে বড় মাত্রায় এগিয়ে দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই ‘খণ্ডযুদ্ধে’ জয় তাদের চূড়ান্ত ‘যুদ্ধে’ বহুমাত্রিকভাবে কাজে লাগবে এবং লাগতে যে শুরুও করেছে, তারই প্রথম প্রকাশ ‘যুগপৎ আন্দোলনে’ এনসিপি ও দেওবন্দি ঘরানার দলগুলোর নাম আসা।
এক সপ্তাহের মধ্যে যে এ রকম দুটি ঘটনা ঘটল, সেটা অস্বাভাবিক নয়। এনসিপির রাজনীতি ও দেশচেতনা এবং দেওবন্দ আলেমদের ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে জামায়াতের এত দিনকার স্পষ্ট অনেক ফারাক ও মতভেদ থাকলেও সেসব অতিক্রম করে সবাই যে কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে, এর স্থানীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক তাৎপর্য বিপুল। এটা ডাকসু-জাকসুর ফলাফলের সঙ্গেও আন্তসম্পর্কিত। সমাজের প্রায় সব সামাজিক ‘শক্তিঘরে’ চব্বিশের আগস্টের পর থেকে সূচিত পরিবর্তনকেও এ ক্ষেত্রে আমরা আমলে নিতে পারি।
ডাকসু নির্বাচনে শিবির জিতেছে এবং বামপন্থী-মধ্যপন্থীরাও কার্যত হারেনি। শেষোক্তরা তাদের বাস্তব সাংগঠনিক শক্তির তুলনায় চমৎকার ফল করেছে। আবার শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তাদের চার দশকের বিবিধ প্রচেষ্টারও সন্তোষজনক উত্তর পেল। কিন্তু উপরিক্ত দুই শক্তির চাওয়া-পাওয়া অতিক্রম করে এই নির্বাচনের মূল অভিঘাত গেছে বাংলামোটরের রূপায়ণ টাওয়ারের অভিমুখে।
এনসিপি গঠিত হয়েছে বেশিদিন হয়নি। শুরু থেকে তাদের প্রধান ও প্রায় একমাত্র শক্তিভিত শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত-ছাত্রসমাজ। জামায়াত-বিএনপি-লীগের বাইরেও ছাত্রসমাজের ভিন্ন কোনো রাজনৈতিক সামাজিক প্রত্যাশা ছিল বলেই গত বছর তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজের ব্যানার ও তা থেকে জন্ম নেওয়া নতুন দলকে পছন্দ করেছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীসমাজ নবগঠিত এই দলের কাছে মোটাদাগে যে আর বড় কোনো প্রত্যাশা করছে না, সেটা ছিল ডাকসু নির্বাচনের প্রধান বার্তা। অথচ এই ক্যাম্পাসই ছিল এনসিপির রাজনৈতিক জন্মস্থান এবং সাংগঠনিক দুর্গ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ৯ সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গত এক বছরের একটা সিরিয়াস মূল্যায়ন হাজির করেছেন, যা এনসিপির জন্য অবজ্ঞা করা কঠিন। এ রকম একটা দুঃসময়ে আটটি দলের যুগপৎ আন্দোলনে অংশ নেওয়া তার জন্য সাংগঠনিক ও রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকার অনিবার্য চেষ্টা হিসেবে দেখা যায়।
কিন্তু তারা প্রকৃতই পুরো দল ঐকমত্যের ভিত্তিতে যুগপৎ আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে বেশ বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই দলের সংগঠকদের বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছে, দলটির তরুণ তাত্ত্বিকেরা জামায়াতের সঙ্গে মিলে যুগপৎ আন্দোলন বিষয়ে টানাপোড়েন ও মতাদর্শিক বিতর্কে পড়েছেন।
আটটি দলের সম্ভাব্য যুগপৎ আন্দোলনের ‘নেতা’ তথা চালকের আসনে যেহেতু জামায়াতে ইসলামীই থাকছে, সে কারণে এনসিপি তাতে শামিল হলে একে সমালোচকেরা প্রথমোক্ত দলের কাছে শেষোক্তদের নীরব এক আদর্শিক আত্মসমর্পণ হিসেবেও দেখতে পারে। আবার তার বিপরীতে এ-ও বলার সুযোগ আছে, যুগপৎ আন্দোলন মানে আদর্শিক অনুমোদন নয়, কর্মসূচিগত সংহতি মাত্র।
অতীতে বাংলাদেশের ইতিহাসে জামায়াতের সঙ্গে বিরোধী আদর্শের দলগুলোর যুগপৎ আন্দোলনের নজির আছে। তবে যুগপৎ রাজনীতি নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্টদের পরস্পরের প্রতি সাংস্কৃতিক অনুমোদনও বটে। গত শতাব্দীর আশির দশকে সামরিক জান্তাবিরোধী যুগপৎ আন্দোলন জামায়াত ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য করেনি। সাংস্কৃতিক অনুমোদন ও রাজনৈতিক পথযাত্রায় সামাজিক বিরোধিতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে করেছিল। তাতে সফলও ছিল তারা। পরবর্তীকালে বিএনপির সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের জোটবদ্ধতাও অনুরূপ বিবেচনাকে গুরুত্ব দিয়েই।
এবারকার যুগপৎ আন্দোলন জামায়াত ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য করছে, এটা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না; যদিও এই যুগপৎ আন্দোলন নির্বাচনী জোট হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার বেশ সম্ভাবনা আছে।
যুগপৎ আন্দোলন কি নির্বাচনী জোটে পরিণত হবে
জামায়াত নতুন ‘যুগপৎ’-এর মাধ্যমে মূলত গত এক বছরের প্রভাবের পরিসর আরও বাড়াতে চাইছে। এনসিপিকে কাছে পেলে তারা নিজেদের রাজনীতিকে আকর্ষণীয় এক তরুণ প্রচ্ছদ দিতে পারে, আবার দেওবন্দি আলেমদের দলগুলো পেয়ে তারা মাওলানা মওদুদীবিরোধী ধর্মতাত্ত্বিক সমালোচনা ও বিরোধের জায়গাও বন্ধ করতে পারবে।
এ রকম ‘যুগপৎ’ তাকে একদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে বাড়তি গতিতে এগোতে সাহায্য করবে, আবার একই সঙ্গে মাদ্রাসাসমাজেও প্রবেশ অবারিত করবে। যেহেতু সম্ভাব্য ‘আট দল’ভুক্তদের মধ্যে আর্থিক, প্রশাসনিক ও কূটনীতিক পরিসরে জামায়াতের ইতিমধ্যে প্রবল শক্তিভিত রয়েছে, ফলে সেই আন্দোলনে তারা নির্দেশকের আসন নিতে পারবে এবং অন্যদের কেবল তাকে অনুসরণ করতে হবে।
গত দশকগুলোয় জামায়াত কেবল অন্যের নেতৃত্বে ‘যুগপৎ’ আন্দোলন করেছে বা জোটবদ্ধ থেকেছে। এবার সে নিজেই এ রকম একটা
উদ্যোগ নিয়ে বড় ধরনের রাজনৈতিক সামর্থ্য দেখাতে চাইতে পারে। তার দিক থেকে এটা সাহসী ইতিবাচক নিরীক্ষাই বটে। যে অবস্থানের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের পুরোনো সমালোচকদের সাংস্কৃতিকভাবে মোকাবিলা করাও তার জন্য সহজ হবে।
তবে সম্ভাব্য এই ‘যুগপৎ’ চরমোনাইপন্থী বা এই কাফেলার অন্য অনেকের জন্য অতটা অস্বস্তিকর হবে না, যতটা হতে পারে এনসিপির অনেক তরুণ সংগঠকের জন্য, যাঁরা এত দিন প্রগতিমুখী ‘মধ্যপন্থা’র কথা বলেছেন।
প্রস্তাবিত যুগপৎ আন্দোলন নির্বাচনমুখী হলে ইসলামী আন্দোলন বা অনুরূপ ধাঁচের দলগুলোর জন্য তাতে সুবিধা রয়েছে। একা নির্বাচন করার চেয়ে এ রকম একটা ‘যুগপৎ’-এর আওতায় নির্বাচনে গেলে তাদের আসন পাওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিতভাবে বাড়বে। এনসিপির জন্যও সেই সম্ভাবনা আছে; যদিও সেটা ক্ষীণ।
ধর্মীয় ধারার দলেগুলোর ভোট যেভাবে সমাজে-পাড়ায়-মহল্লায় লেনদেন হতে পারে, তাদের সঙ্গে সেভাবে নড়াচড়া না-ও করতে পারে। জামায়াত ও কওমি ঘরানার দলগুলোর ভোটের সুস্পষ্ট সামাজিক চরিত্র রয়েছে। আবার এ রকম একটা যুগপৎ আন্দোলন এবং বিশেষভাবে
নির্বাচনী আসন সমঝোতার বিপরীতে এনসিপিকে আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আপস করতে হবে বিপুল। ইসলামী আন্দোলন বা অনুরূপ দলগুলোকে সেটা করতে হবে না।
নিশ্চয়ই এনসিপির তাত্ত্বিক ও মুরব্বিদেরও এ রকম পরিস্থিতি বিবেচনায় রয়েছে। সে জন্যই হয়তো যুগপৎ আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশমাত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এনসিপি ঘরানার আইডিগুলোয় এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক ছড়িয়েছে।
সংগঠকদের মধ্যে যারা এই কৌশলের পক্ষে, সে রকম নেতৃত্ব মনে করছে, গণ-অভ্যুত্থানের প্রধান এজেন্সি হিসেবে এককভাবে দীর্ঘ ম্যাচের ধৈর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে নির্বাচনের আগেই একটা শক্ত দর-কষাকষির জন্য যুগপৎধর্মী যৌথতায় লাভ বেশি হবে। বলা বাহুল্য, এ রকম ‘অঙ্ক’ নতুন সংসদে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থানে শক্তি জোগাবে। জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধের দাবির সঙ্গে এসব অঙ্কের কোনো দূরবর্তী যোগাযোগ আছে কি না, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সামনে সেটাও কৌতূহলোদ্দীপক এক বিষয় হয়ে উঠেছে।
● আলতাফ পারভেজ গবেষক