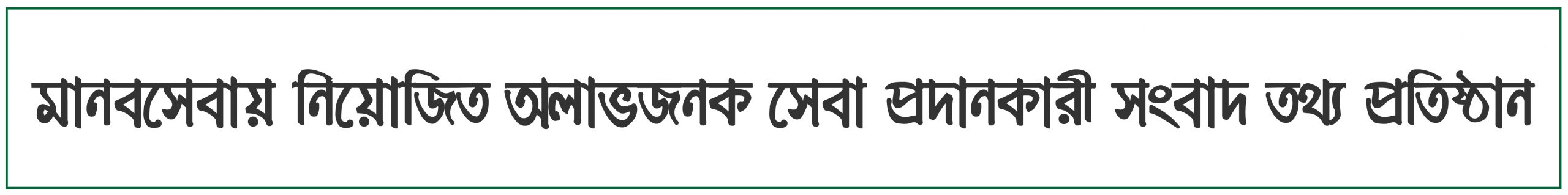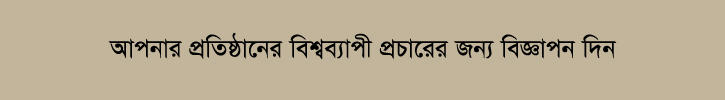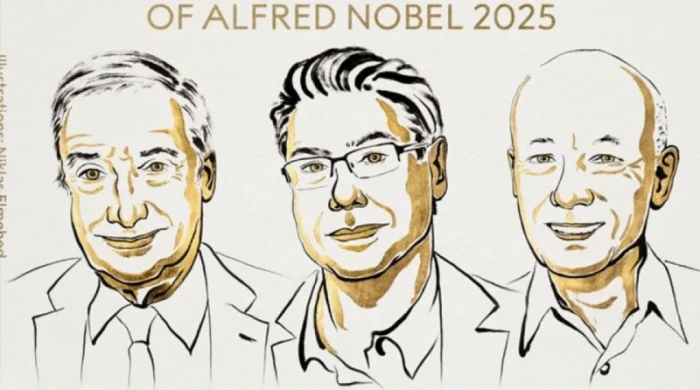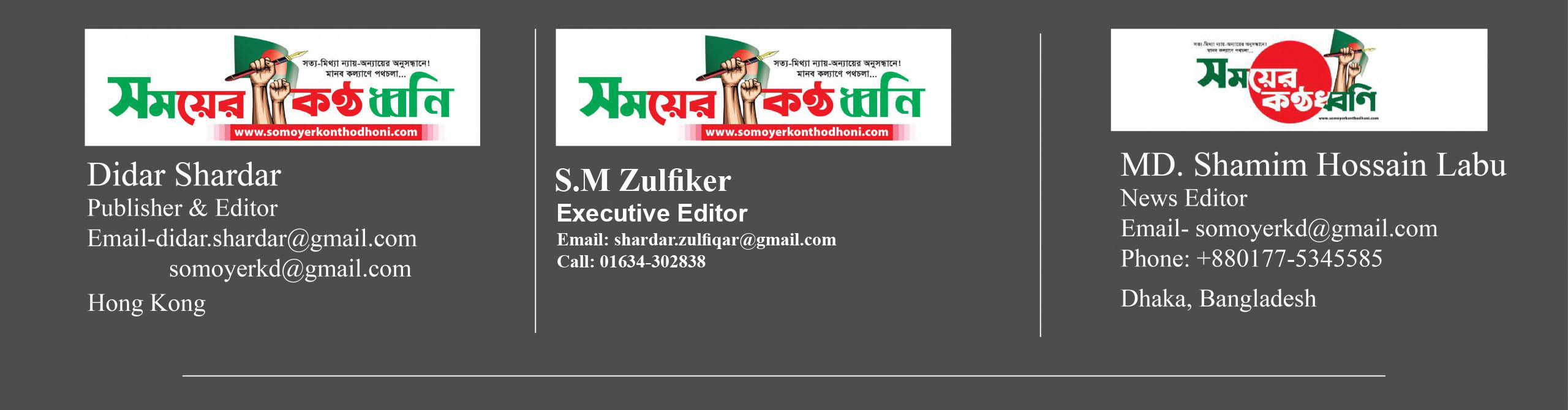মহালয়া: আজ দেবীপক্ষের শুভ সূচনা
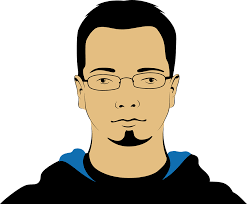
- আপডেট টাইম : রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
- ২৬ বার পঠিত

মহালয়া সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য এক বিশেষ ও তাৎপর্যময় দিন। আশ্বিন মাসের অমাবস্যা তিথিতে পালিত এই দিনটিকে শারদীয় দুর্গোৎসবের মূল সূচনা হিসেবে ধরা হয়।
মহালয়ার মধ্য দিয়েই পিতৃপক্ষের সমাপ্তি ঘটে এবং দেবীপক্ষের শুভ সূচনা হয়। তাই একদিকে যেমন এটি পূর্বপুরুষদের স্মরণের দিন, অন্যদিকে দেবী দুর্গার পৃথিবীতে আগমনের আনন্দঘন আহ্বানও বটে।
মহালয়ার তাৎপর্য ও আধ্যাত্মিক দিক
হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, মহালয়ার দিনে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ বা শ্রাদ্ধ করলে তাঁদের আত্মা তুষ্ট হন এবং পরিজনদের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। এজন্য ভোরবেলা নদী, পুকুর বা অন্য কোনো জলাশয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করার প্রচলন আছে। তর্পণ শুধু একটি আচার নয়, এটি পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও এক গভীর মাধ্যম।
অন্যদিকে, মহালয়াকে কেন্দ্র করে ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে, এই দিন দেবী দুর্গা কৈলাস পর্বত ছেড়ে তাঁর পিতৃগৃহে—অর্থাৎ পৃথিবীতে—অবতরণের প্রস্তুতি নেন। সেই কারণে মহালয়া মানেই পিতৃপক্ষের সমাপ্তি নয়, বরং দেবীপক্ষের আনন্দঘন সূচনার প্রতীক।
মহালয়া ও দুর্গাপূজা: ভোরের মহিষাসুরমর্দিনী
বাংলার মানুষের কাছে মহালয়ার ভোর এক বিশেষ আবেগের নাম। সূর্য ওঠার আগেই রেডিও-টেলিভিশনের পর্দায় শুরু হয় মহিষাসুরমর্দিনী সম্প্রচার। চণ্ডীপাঠ, স্তোত্রপাঠ, সংগীত ও আবৃত্তির সংমিশ্রণে নির্মিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি ভক্তদের জন্য এক অনন্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তৈরি করে। শিশুরা থেকে বৃদ্ধ সবাই ভোরে উঠে শ্রবণ করেন দেবীকে আহ্বান জানানোর এই আয়োজন।
এই অনুষ্ঠান কেবল ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত নয়, এটি বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনারও অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। মহালয়ার ভোর মানেই রেডিওর শব্দে মগ্ন হয়ে থাকা এক অন্য রকম অনুভূতি, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে আছে।
বাংলা সংস্কৃতিতে মহালয়ার প্রভাব
মহালয়া শুধু একটি ধর্মীয় দিন নয়, এটি বাঙালির আবেগ ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। এদিন থেকেই শুরু হয় দুর্গোৎসবের মূল আমেজ। নতুন জামাকাপড় কেনাকাটা, মণ্ডপ সজ্জা, আলোকসজ্জা ও পূজা-উৎসবের প্রস্তুতি মহালয়ার দিন থেকেই গতি পায়।
সাহিত্য, সংগীত, নাটক, আবৃত্তি ও চিত্রকলায় মহালয়ার আবহ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। অনেক কবিতা, গান ও নাটকে মহালয়ার ভোরের আবেগকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে কালজয়ী সৃষ্টি। ফলে মহালয়া শুধু একটি ধর্মীয় উপলক্ষ নয়, বরং বাংলা সংস্কৃতির এক চিরন্তন উৎসব আহ্বান।
মহালয়ার শিক্ষণীয় দিক
মহালয়ার গুরুত্ব কেবল আচার-অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে রয়েছে গভীর মানবিক শিক্ষা।
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ: তর্পণের মাধ্যমে আমরা শিখি পূর্বপুরুষদের স্মরণ করতে এবং তাঁদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে।
আধ্যাত্মিকতা: দেবী দুর্গার আগমন বার্তা মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ করে এবং জীবনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার গুরুত্ব মনে করিয়ে দেয়।
ন্যায়ের জয়: মহিষাসুরমর্দিনীর কাহিনি আমাদের শেখায়—অসুর শক্তি যত প্রবলই হোক না কেন, সত্য ও ন্যায় সর্বদা বিজয়ী হয়। এই শিক্ষা আজকের সমাজেও সমানভাবে প্রযোজ্য।
আধুনিক সমাজে মহালয়া
বর্তমান যুগে প্রযুক্তি ও আধুনিকতার ভিড়েও মহালয়ার গুরুত্ব কমেনি। বরং মহালয়ার ভোরে টেলিভিশন, ইউটিউব বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মহিষাসুরমর্দিনী শোনা বা দেখা এখন অনেক পরিবারের একটি নিয়মিত অংশ হয়ে গেছে। শহর থেকে গ্রাম—সবখানেই মহালয়ার আমেজ বাঙালির হৃদয়ে একই আবেগ ছড়িয়ে দেয়।
তাছাড়া, মহালয়াকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা শুভেচ্ছা বিনিময়, ছবি ও ভিডিও শেয়ারও এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। ফলে মহালয়া একদিকে ঐতিহ্যের ধারক, অন্যদিকে আধুনিকতার সেতুবন্ধনও বটে।
উপসংহার
মহালয়া কেবল একটি ধর্মীয় দিন নয়, এটি এক আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক অনুভূতির সমন্বয়। এদিন ভক্তরা যেমন দেবী দুর্গার আগমনের আনন্দে মাতোয়ারা হন, তেমনি পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে নিজেদের শেকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করেন। মহিষাসুর বধের প্রতীকী বার্তা মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা দেয়।
তাই মহালয়া আজও বাঙালির সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে আছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মহালয়ার আবেগ ও মাহাত্ম্য অটুট থেকে যাবে, ভোরের মহিষাসুরমর্দিনী সুরের মতোই চিরন্তন হয়ে।