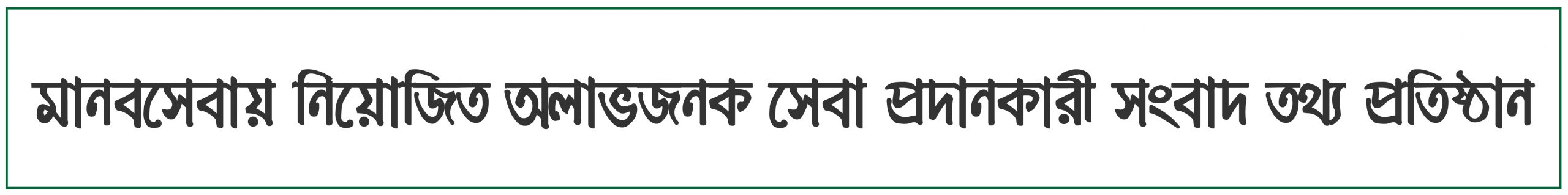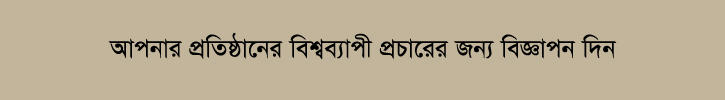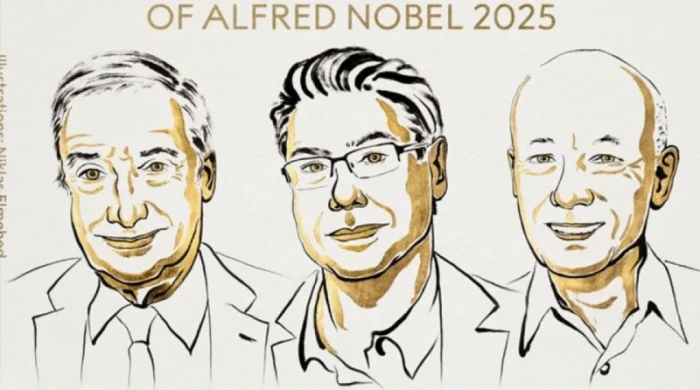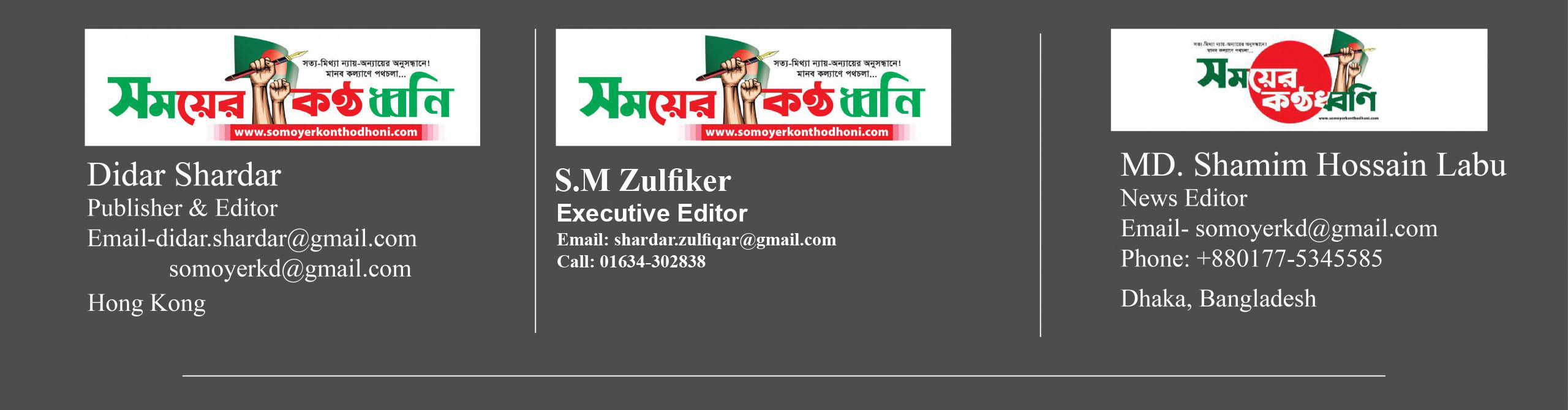কমছে কৃষিজমি প্রয়োজন সময়োপযোগী ভূমি নীতি
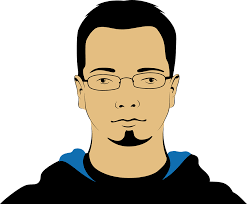
- আপডেট টাইম : বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
- ১৬ বার পঠিত

বাংলাদেশ একসময় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল কৃষকের ঘামঝরা পরিশ্রমে। অথচ আজ সেই সোনার জমি হুমকির মুখে। প্রতিদিন হারাচ্ছি গড়ে ২১৯ হেক্টর কৃষিজমি। জনসংখ্যা ও নগরায়ণের চাপে আবাদযোগ্য জমি পরিণত হচ্ছে আবাসন প্রকল্প, কল-কারখানা, সড়ক, ব্রিজ, ইটভাটার চরে। সরকারি হিসাবে প্রতিবছর প্রায় ৭০-৮০ হাজার হেক্টর জমি চলে যাচ্ছে অকৃষি খাতে। স্বাধীনতার পর যেখানে দেশে কৃষিজমি ছিল ২ কোটি ১৭ লাখ হেক্টরের বেশি, বর্তমানে তা নেমে এসেছে ৮০ লাখ হেক্টরের নিচে। খাদ্য উৎপাদনে যে আত্মনির্ভরশীলতা ছিল, তা এখন বিপদের মুখে।
বাংলাদেশের মতো কৃষিনির্ভর দেশে কৃষিজমির সঙ্কোচন মানে হলো খাদ্য ঘাটতি, আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে চাপ, কৃষি পেশা থেকে মানুষের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের জন্ম নেওয়া।
নওগাঁ, দিনাজপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, এমনকি রাজধানী ঢাকার আশপাশেও কৃষিজমি হারানোর হার উদ্বেগজনক। নওগাঁ জেলায় ২০১৫ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত আবাদি জমি কমেছে ১২ হাজার হেক্টরের বেশি। অথচ এখানকার ভূমি একসময় ছিল দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনের অন্যতম ভরসা। চট্টগ্রাম অঞ্চলে গত এক দশকে কৃষিজমি কমেছে ৫২ হাজার একর, খুলনায় কমেছে ১৫ হাজার হেক্টর। কৃষকরা জমি বিক্রি করে চলে যাচ্ছেন অন্য পেশায়; মূলত উৎপাদন খরচ বাড়লেও কৃষিপণ্যের দাম না বাড়ায় কৃষি পেশা আর লাভজনক থাকছে না।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা দুরূহ হয়ে উঠবে। হাইব্রিড প্রযুক্তি, উন্নত বীজ ও গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদন সাময়িকভাবে বাড়লেও, কৃষিজমি কমে যাওয়ার কারণে এই উৎপাদন টেকসই রাখা যাচ্ছে না। উৎপাদন খরচ ৩.৫ শতাংশ বাড়লেও কৃষিপণ্যের দাম বেড়েছে মাত্র ১.৩১ শতাংশ। ফলে কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, যার পরিণতি হিসেবে জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন।
একই সঙ্গে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যও হুমকির মুখে। বনভূমি ২০১৫ থেকে ২০২৩ সময়কালে কমেছে ৫.৪১ শতাংশ। প্রাকৃতিক বন হারিয়ে যাচ্ছে, সামাজিক বনায়ন তার বিকল্প হতে পারছে না। এতে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।
বাংলাদেশে জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনি কাঠামো থাকলেও তা বাস্তবায়নের অভাবে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। ‘জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০১০’ ও ‘কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি জোনিং আইন ২০১০’ অনুসারে কৃষিজমি ভরাট করে বাড়ি, শিল্প-কারখানা নির্মাণ নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবে এর বিপরীত চিত্রই বেশি দেখা যায়।
এখন সময় এসেছে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার। প্রথমত ফসলি জমিতে শিল্প-আবাসন প্রকল্প সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত উপজেলায় পরিকল্পিত স্যাটেলাইট শহর গড়ে তুলতে হবে, যাতে নগরায়ণের চাপ কেন্দ্রীভূত না হয়। তৃতীয়ত কৃষিজমি ক্রয়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ (সিলিং) আরোপ করা দরকার, কেউ যেন নির্দিষ্ট সীমার বাইরে জমি কিনতে না পারে। এতে ভূমি দখলবাজদের দৌরাত্ম্য কমবে এবং কৃষকের জমি রক্ষা পাবে।
সরকারি খাসজমি চিহ্নিত করে তা কৃষির আওতায় আনাও এখন সময়ের দাবি। পুরনো ভিটায় বহুতল ভবনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কৃষকদের শূন্য সুদের ঋণ দেওয়া যেতে পারে। এতে করে পরিবারভিত্তিক জমি ভাগ হয়ে নতুন বসতভিটার প্রবণতাও কমবে।
সবচেয়ে বড় কথা, কৃষকের উৎপাদন খরচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষিপণ্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। কৃষক বাঁচলেই কৃষি বাঁচবে, আর কৃষি বাঁচলেই দেশ খাদ্যে স্বনির্ভর থাকবে। কৃষিজমি এখন শুধু একটি সম্পদ নয়- এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বেঁচে থাকার ভিত্তি। তাই জমির ধ্বংসের এই হুমকিকে ঠেকাতে চাই কার্যকর ভূমি নীতি এবং তা বাস্তবায়ন; ভূমি রক্ষায় এর বিকল্প নেই।