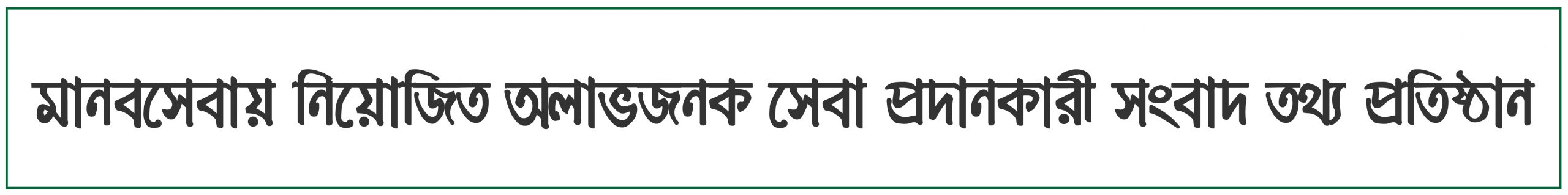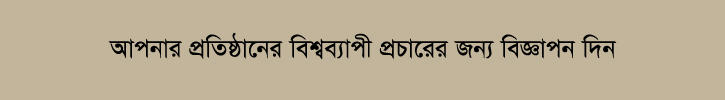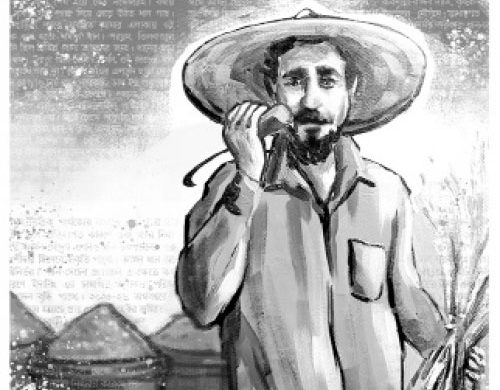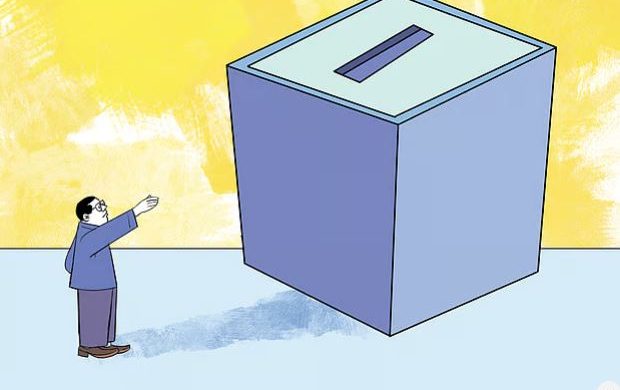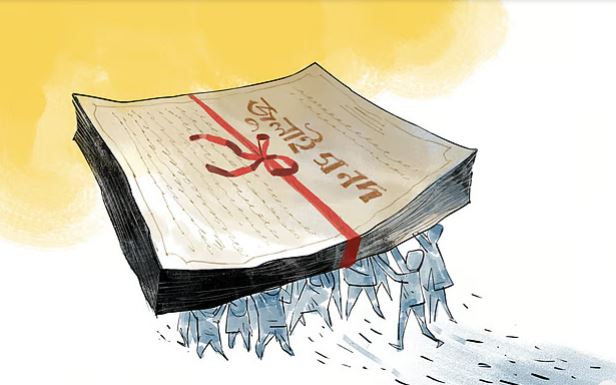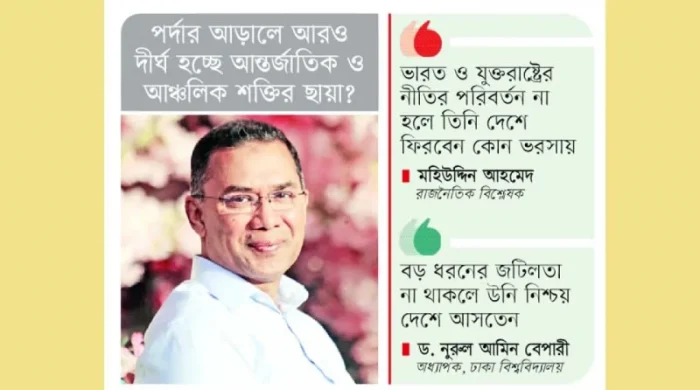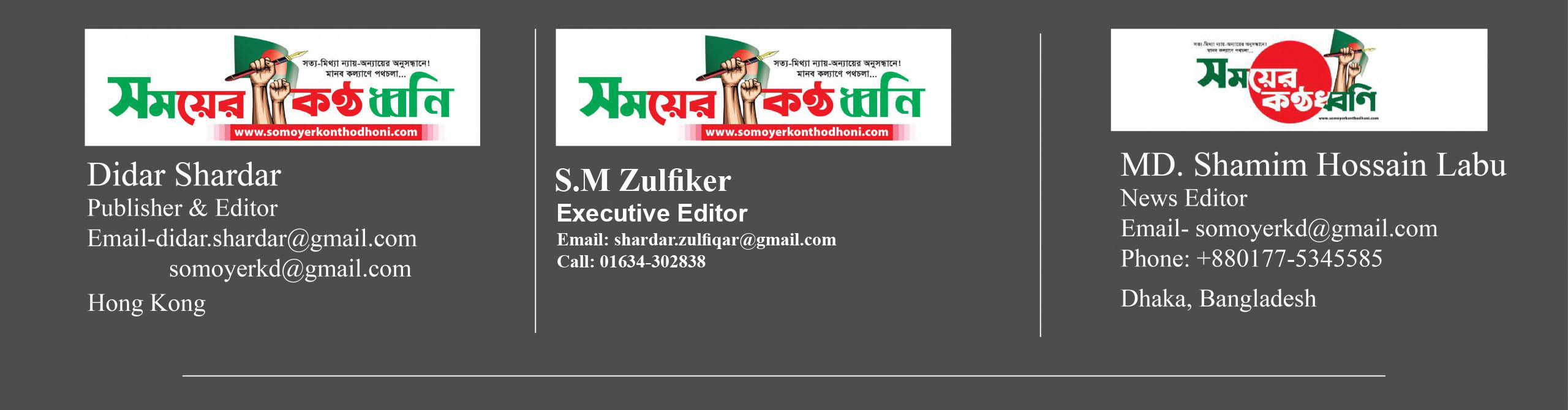রাজনীতি’র উদ্দেশ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল
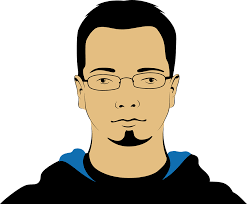
- আপডেট টাইম : সোমবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৫
- ২১ বার পঠিত

১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্টে পাকিস্তান স্বাধীন হলো এবং উভয় রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা ঘটল বুর্জোয়াদের শাসন। এই শাসকরা সামাজিক বিপ্লব চাইবেন কেন? তাদের সার্বিক প্রচেষ্টা ছিল তেমন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নির্মূল করা। পূর্ববঙ্গে যা ঘটেছে, সেটা তো আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভেতরে রয়েছে। সাতচল্লিশের দেশভাগ মুসলিম লীগকে যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা এনে দিয়েছে, তার চেয়ে বহুগুণ অধিক ক্ষতি করেছে কমিউনিস্টদের। এমনকি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বিরোধী ছিল যে কংগ্রেস, তাদের তুলনাতেও কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষতি ও বিপদ ছিল অনেক বেশি। নতুন শাসকদের মনে সামাজিক বিপ্লবের সেই পুরনো শঙ্কা কমেনি, হঠাৎ করে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রাপ্তিতে তা বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্র তার নিজের সব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর। সদস্য, সমর্থক ও সহানুভূতিশীলদের অনেকেই দেশত্যাগ করেছেন; সক্রিয়রা কেউ বন্দি হয়েছেন কারাগারে, বহুসংখ্যক গ্রেপ্তার এড়িয়েছেন আত্মগোপন করে। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের নাস্তিক বলেও প্রচার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে নাস্তানাবুদ দশা। পাকিস্তান রাষ্ট্রে যে পূর্ববঙ্গের মানুষের মুক্তি আসবে না, সেটা পরিষ্কার হতেও অবশ্য বেশি সময় লাগেনি। মানুষ পোস্ট অফিসে গেছে মানি অর্ডার করবে বলে, দেখে ফর্মে ইংরেজি আছে উর্দুও আছে, বাংলা নেই। ডাকটিকিটে, পোস্টকার্ডে, পোস্টাল খামেরও একই দশা। ওদিকে রাষ্ট্রপতির পদে আসীন এবং জাতির পিতা বলে সম্মানিত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ঢাকায় তার প্রথম সফরে এসে স্বকণ্ঠে ও সদম্ভে ঘোষণা দিলেন যে, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। পূর্ববঙ্গের মানুষ মর্মাহত হলো। তারা দেখল যে, রাষ্ট্রের জনসংখ্যার ৫৬ জনের মাতৃভাষা বাংলা এবং মূলত বাঙালিদের ভোটেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, সেই রাষ্ট্রে তারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে যাবে। ইংরেজের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে পড়বে উর্দুর খপ্পরে।
জিন্নাহ সাহেব উর্দুকে কেন রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলেন? সেটা তো তার মাতৃভাষা নয়, তার মাতৃভাষা গুজরাটি। চাইলেন এই জন্য তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের পুরনো ভিত্তির ওপর বাস্তবের পাকিস্তান রাষ্ট্রকে মজবুত করা যাবে না। ওই জ্ঞান থেকে তিনি গণপরিষদের একেবারে প্রথম অধিবেশনেই ঘোষণা দিয়েছিলেন নতুন রাষ্ট্রে কেউ পাঞ্জাবি, কেউ বাঙালি, কেউ সিন্ধি এসব থাকবে না। সবাই হবে অভিন্ন একটি নতুন জাতির সদস্য এবং সে জাতি হলো পাকিস্তানি জাতি। নতুন জাতি গঠন করেই পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে হবে, এই ছিল তার বিশ্বাস। জিন্নাহ আধুনিক মানুষ ছিলেন। ধর্ম নয়, ভাষাই যে জাতি গঠনের প্রধান ভিত্তি, এ সত্য তার জানা ছিল। সে জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভাষাভিত্তিক একাধিক জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে প্রারম্ভেই প্রতিহত করে, উর্দু ভাষাকে ভিত্তিতে রেখে পাকিস্তানি পরিচয়ে একটি নতুন জাতি গঠন করাই ছিল তার লক্ষ্য। জাতি গঠনের জন্যই রাষ্ট্রভাষা একাধিক নয়, হবে একটিই এবং সেটা অবশ্যই বাংলা হবে না হবে উর্দু। এই ছিল তার সিদ্ধান্ত। উর্দু পাকিস্তানে বসবাসকারী শতকরা ৫ জনেরও যে মাতৃভাষা নয় এটা সত্য হলেও, উর্দু ছিল অবাঙালি পাকিস্তানিদের যোগাযোগ, এমনকি সাহিত্যেরও ভাষা। তদুপরি অবাঙালি পাকিস্তানি মুসলমানরা মনে করত, উর্দু তাদের সম্পত্তি ও সম্পদ। কাজেই রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষের ভাষা বাংলা হলেও বাংলা দিয়ে কাজ হবে না, এমনই ছিল তাদের বোধ।
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যেভাবে বলত যে, ভারতবর্ষ হচ্ছে এক জাতির দেশ। জিন্নাহ সাহেবও তেমনি চেয়েছিলেন, পাকিস্তানকে এক জাতির দেশে পরিণত করতে। ভারতবর্ষ যে এক জাতির নয় বহুজাতির দেশ, সেটা কংগ্রেসীরা স্বীকার করেনি। পাকিস্তানেও যে পাঁচটি স্বতন্ত্র জাতির বসবাস, সেটা মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মানতে প্রস্তুত ছিল না। জিন্নাহ এবং তার সহযোগী রাজনীতিক ও আমলারা পাকিস্তানকে কেবল যে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা-ই নয়, তাদের অভিপ্রায় ছিল, রাষ্ট্রটি হবে পুঁজিবাদী ধরনের। জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে অমনটাই চাওয়া স্বাভাবিক। জওহরলাল নেহরু সমাজতন্ত্রে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু তার শাসনাধীনেও রাষ্ট্র হিসেবে ভারত পুঁজিবাদী পথ ধরেই এগিয়েছে। আর মহাত্মা গান্ধী তো, কেবল যে সমাজতন্ত্রবিরোধী ছিলেন তা-ই নয়, তিনি চান বা না-চান রামরাজ্যের আবরণে তার অনুগামীরা একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। ওই পথেই তারা এগিয়েছেন। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতার দুদিন পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ যে ভাষণটি দেন, তাতে শুধু যে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণারই পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন তা-ই নয়, নতুন রাষ্ট্র তরুণদের সামনে ব্যক্তিগত উন্নয়নের যে স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তার কথাও বলতে ভোলেননি। বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন করাচির এক যুবকের, চার বছর আগে যিনি মাসে বেতন পেতেন ২০০ টাকা এখন পাচ্ছেন দেড় হাজার। তার পরামর্শ ছিল, রাষ্ট্রভাষা কী হবে না হবে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, তরুণরা যেন নতুন রাষ্ট্র তাদের জন্য যে সুযোগ এনে দিয়েছে তার সদ্ব্যবহার করে। পথ ধরে পুঁজিবাদী উন্নয়নের অভিমুখে। রেসকোর্স এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল, উভয় স্থানেই তরুণদের তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন শিশু রাষ্ট্র পাকিস্তানের শত্রুদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে। প্রধান শত্রু যে কমিউনিস্টরাই সেটা তার বক্তব্যে ছিল। কমিউনিস্টরা শত্রু কেন? কোন কারণে? কারণটা এই যে, তারা পুঁজিবাদবিরোধী। ভীষণ রকমের পাকিস্তানবিদ্বেষী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও কিন্তু কমিউনিস্টদের এক নম্বরের শত্রু জানতেন এবং সেটাও ওই একই কারণে; পুঁজিবাদী উন্নয়নের মাধ্যমে নিরুপদ্রবে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার অভিলাষে। হিন্দুস্থানে পাকিস্তানে যতই বিরোধ থাক, পুঁজিপন্থি জাতীয়তাবাদীরা যে একই পথের পথিক হবেন সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। প্যাটেল, গান্ধী, জিন্নাহ কেউই ভুল করেননি। শত্রুকে তারা সঠিকভাবেই চিহ্নিত করে ফেলেছিলেন। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে যে অভ্যুত্থান ঘটে, তাতে চালিকাশক্তি ছিলেন বামপন্থিরা। পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে যত আন্দোলন হয়েছে, সবকটিতেই বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্ব যদিও দৃশ্যমান ছিল, তবু মূল কাজটা করতে হয়েছে বামপন্থিদেরকেই। ঊনসত্তরের অভ্যুত্থান ঘটত না, যদি না বামপন্থি তরুণরা এগিয়ে আসত এবং মওলানা ভাসানী সামনে এসে না দাঁড়াতেন। ওই অভ্যুত্থান স্বাধীনতার তো বটেই, পূর্ববঙ্গের জন্য মুক্তির আন্দোলনেই পরিণত হচ্ছিল। আওয়াজ উঠেছিল, স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার। শেখ মুজিব নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সম্ভব হলে সমগ্র পাকিস্তানের, ব্যর্থ হলে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন, এটাই ছিল তার নিজের এবং তার অনুসারীদের আকাক্সক্ষা। মুজিব যে ক্ষমতার জন্যই রাজনীতি করেন, সে ব্যাপারটা অন্যরা বুঝুক না বুঝুক মুজিব নিজে ঠিকই জানতেন। জিন্নাহ যেমন চেয়েছিলেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল অন্য কেউ নন, তিনি নিজেই হবেন; মুজিবও তেমনি নিজেকেই রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে দেখতে পছন্দ করতেন। তার ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে ক্ষমতায় যাওয়ার আগ্রহের কথাটা পরিষ্কারভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। ১৯৫০ সালে, যখন তিনি জেলখানায়, ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে, তখন জেল পরিদর্শন করতে এসে একজন চিকিৎসক শেখ মুজিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি কেন জেল খাটছেন? উত্তরে মুজিব বলেছিলেন, ‘ক্ষমতা দখলের জন্য’। চিকিৎসকের পরবর্তী প্রশ্ন, ক্ষমতা দখল করে কি করবেন? শেখ মুজিবের জবাব ছিল, ‘যদি পারি দেশের জন্য কিছু করব। ক্ষমতায় না গেলে, কি তা করা যায়’? শুনে চিকিৎসক বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, এমন সোজা কথা তিনি অন্য কোনো রাজবন্দির মুখে শোনেননি। (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১৮৫) শেখ মুজিব সেদিন যা বলেছিলেন সেটা কিন্তু তার একার নয়, সব জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকেরই মনের কথা। কথাটা তারা প্রকাশ্যে বলেন না, মুজিবের সৎসাহস ছিল, তিনি বলেছেন।
জাতীয়তাবাদীরা দেশের মানুষের কথা যে ভাবেন না, তা নয়। তবে নিজেদের ক্ষমতায় যাওয়ার ব্যাপারটাকেই সর্বাগ্রে স্থান দেন। ‘রাজনীতি’ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার জন্যই। সেটা জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতন্ত্রীরাও চান। তবে জাতীয়তাবাদীরা চান নিজেদের জন্য, সমাজতন্ত্রীরা চান সমাজের সব মানুষের জন্য। পার্থক্যটা ওইখানেই এবং সে পার্থক্য সামান্য নয়। মৌলিক বটে। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল তার কারণ অন্যকিছু নয়, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ছাড়া। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পূর্ববঙ্গের জন্য স্বাধীনতা চেয়েছিল, সেটা ছিল জাতীয়তাবাদী আকাক্সক্ষা; সে অভ্যুত্থান কিন্তু শুধু জাতির মুক্তি চায়নি, মানুষের মুক্তিও চেয়েছিল, যেটা ছিল সমাজতান্ত্রিক আকাক্সক্ষা। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বামপন্থিরা গোলটেবিল বর্জন করে আন্দোলনকে আরও সামনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, মুজিব সেটা চাননি; তিনি গোলটেবিলে গেছেন এবং নির্বাচনের আয়োজন করা হচ্ছে দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নির্বাচনে যে জনগণের মুক্তি আসবে না, শাসক বদলাবে, শাসন-শোষণ বদলাবে না, সে-কথা মওলানা স্পষ্ট করে বলেছিলেন। তার অনুসারীরা পূর্ববঙ্গে নির্বাচন বর্জনও করেছেন। মুজিবের জাতীয়তাবাদী পথ ছিল আপসপন্থি এবং নির্বাচনে বিশ্বাসী। নির্বাচনে যাচ্ছেন অথচ মানুষের মুক্তির যে আকাক্সক্ষা জেগে উঠেছে, সেটাকে তো উপেক্ষা করা যাবে না, গোঁজামিল দিয়ে তাই সমাজতন্ত্রের কথা বলা। কিন্তু শেখ মুজিব এটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে তার সমাজতন্ত্র বিদেশি ধরনের হবে না, হবে নিজেদের দেশের। জাতীয় সমাজতন্ত্রের এই ধারণাটা নতুন কিছু নয়, এটা হিটলার এবং মুসোলিনির কণ্ঠে আগেই শোনা গেছে।
স্মরণীয় যে, মুসোলিনি সমাজতন্ত্রীদের দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। আর মেহনতি মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য হিটলার তো তার পার্টির নামই রেখেছিলেন ‘ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি’। শেখ মুজিবও মুখে সমাজতন্ত্রী ছিলেন বটে, তবে অন্তরে ছিলেন ব্যক্তিগত ক্ষমতা লাভে বিশ্বাসী। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের সেই বিখ্যাত বক্তৃতার শুরুতেই ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জিতেও তারা যে ‘গদি’তে বসতে পারেননি, সেটা নিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং তিনি যদি ‘হুকুম’ দিতে না পারেন তাহলেও জনতা যেন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলে, সে আহ্বান জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য, হুকুম অন্য কেউ দিতে পারবেন না, তিনি ছাড়া। বায়ান্নতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং ঊনসত্তরে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব ছিল সর্বদলীয়, একাত্তরে এসে মুজিব আহ্বান জানালেন পাড়া-মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের। তিনি যে সমাজতন্ত্রী নন, জাতীয়তাবাদীই রয়ে গেছেন, সেটা বোঝার জন্য অতিরিক্ত প্রমাণের আবশ্যক ছিল না। অথচ হানাদার বাহিনী যখন গণহত্যার জন্য সব আয়োজন চূড়ান্ত করছিল, তখন সে খবর জানা সত্ত্বেও প্রতিরোধের ব্যাপারে প্রকাশ্যে তো নয়ই, কোনো গোপন নির্দেশনাও তিনি দেননি। যুদ্ধ শুরু হয়েছে প্রতিরোধের প্রয়োজনে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে। মুজিব নিজে যুদ্ধে যোগ দেবেন কী, হানাদারদের হাতে বন্দি হতে গররাজি হলেন না। হানাদাররা তাকে নিয়ে গেল পাকিস্তানে, অবশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতারা দিশেহারা অবস্থায় যা করা সম্ভব ছিল তা-ই করলেন, আশ্রয় নিলেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধ করলেন সাধারণ মানুষ, যাদের বেশিরভাগই কৃষক পরিবারের সদস্য। সমাজতন্ত্রীদের অধিকাংশই দেশের ভেতরেই রয়ে গেলেন এবং বিভিন্ন এলাকায় হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। কলকাতায় গিয়ে জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ প্রবাসী সরকার গঠন করেছে; যুদ্ধ পরিচালনাও সেই সরকারই করেছে, কিন্তু মূল নেতা শেখ মুজিব উপস্থিত না থাকায় তাদের কাজ নানাভাবে বিঘ্নিত হয়েছে এবং বিভিন্ন রকম ও মাত্রায় কোন্দল দেখা গেছে। অনেকেই কান্নাকাটি করেছেন, কেউ কেউ ভোগবিলাসের মওকা খুঁজেছেন। মূলত তাজউদ্দীন আহমদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল অনেক ত্যাগ-আত্মত্যাগে।