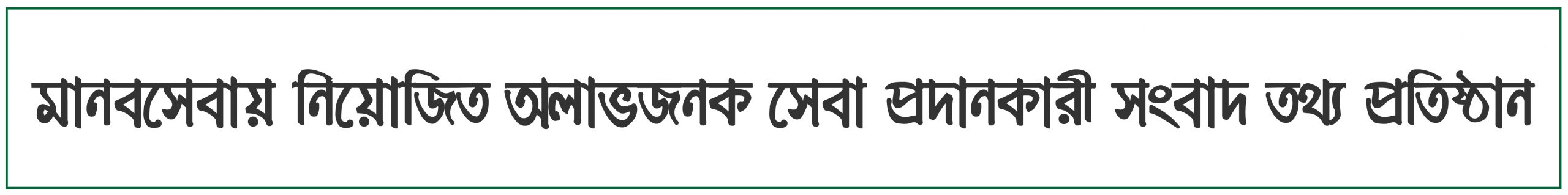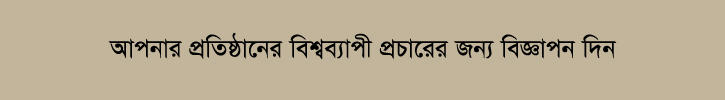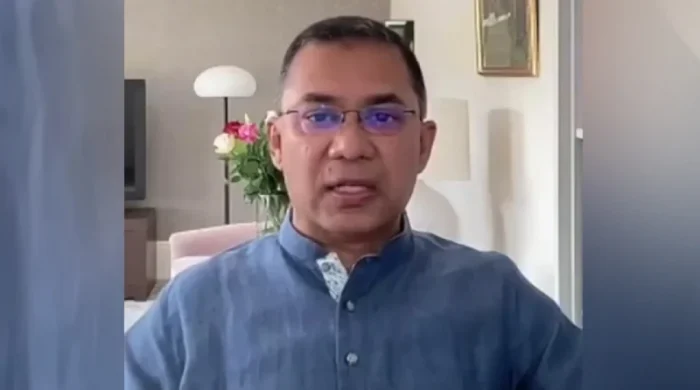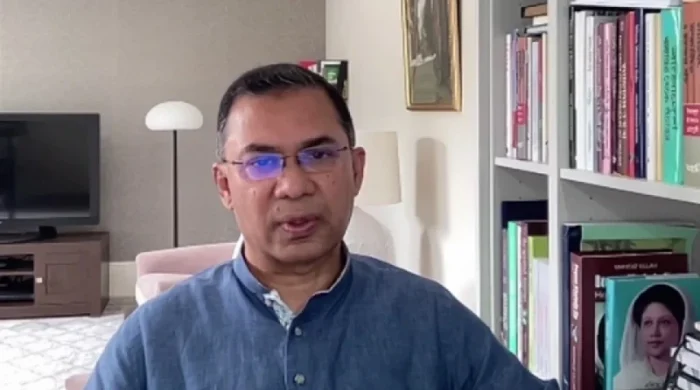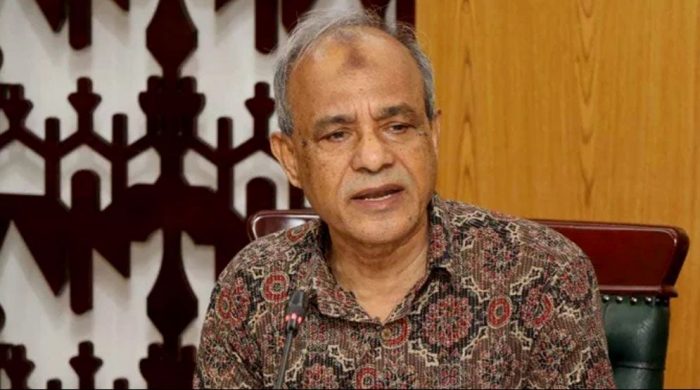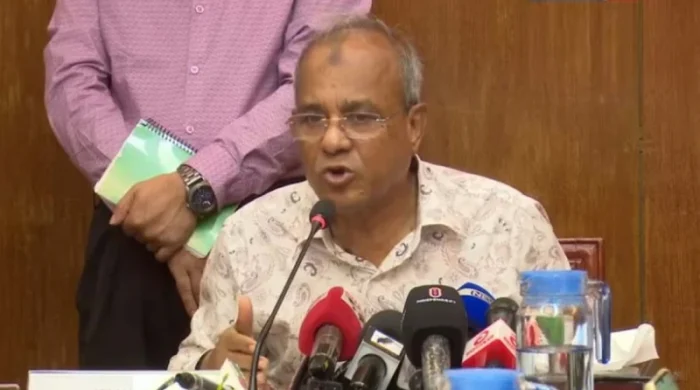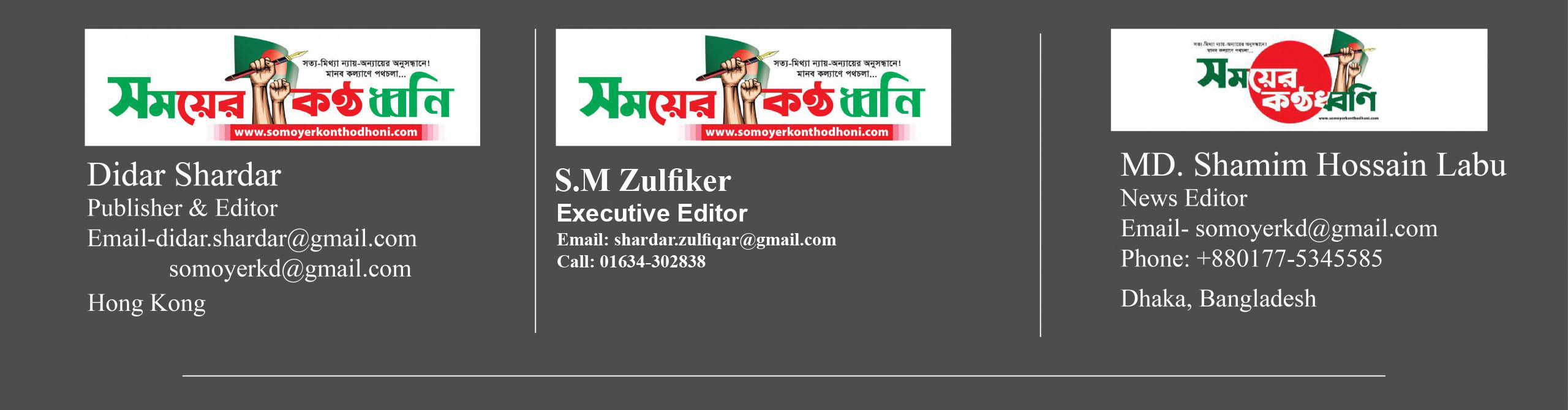ক্রিপ্টোকারেন্সি হতে পারে স্বপ্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মুদ্রা ডলারের বিকল্প
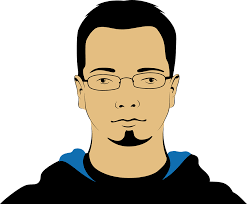
- আপডেট টাইম : রবিবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২
- ১৬০ বার পঠিত

বর্তমান বিশ্বের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, সিঙ্গাপুর, হংকংসহ অনেক দেশের মুদ্রার নাম ডলার হলেও আমরা মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলারকে বোঝাতে চাচ্ছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে একটি দেশ। এই দেশগুলোর প্রত্যেকের একটি স্বতন্ত্র মুদ্রা রয়েছে অথচ কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা। কিভাবে একটি দেশের মুদ্রা বিশ্বের সব দেশের মুদ্রার ওপর জেঁকে বসল, কিভাবে এই ডলার বিশ্বকে শাসন-শোষণ করছে এবং কিভাবে এর থেকে উত্তরণ পাওয়া যায় সে বিষয় নিয়েই আজকের আলোচনা।
উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশ্বে মূলত যে তিন ধরনের মুদ্রার প্রচলন দেখা গেছে তার অন্যতম হলো কমোডিটি কারেন্সি, যার রয়েছে অন্তর্নিহিত মূল্যমান, যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র। প্রাচীনকাল থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ইত্যাদি সরাসরি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রাকে গলিয়ে ফেললেও এর মূল্য হ্রাস পায় না, এ জন্য স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা হলো কমোডিটি মানি। মানব ইতিহাসের বড় একটি সময়জুড়ে অর্থনৈতিক লেনদেন এর জন্য সোনা, রুপা ও তামা কমোডিটি কারেন্সি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
পরবর্তীতে প্রকৃত মূল্যবান বস্তুর সহজ ব্যবহারযোগ্যতার কিছু সীমাবদ্ধতার অজুহাতে বিকল্প হিসেবে রিপ্রেজেন্টেটিভ কারেন্সি অর্থাৎ কাগজের মুদ্রার যাত্রা শুরু হয়। কাগজের মুদ্রার কোনো অন্তর্নিহিত মূল্য নেই। তবে এই কাগজের মুদ্রা কোনো মূল্যবান ধাতু বিশেষ করে স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। এই কাগজের মুদ্রার মান নির্ভর করে কোনো রাষ্ট্রের স্বর্ণের মজুদের ওপর, ফলে এই কাগজের মুদ্রা স্বর্ণমান বা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করে। চীন সর্বপ্রথম এই কাগজের নোটের প্রচলন করে তবে ইউরোপে এই নোটের প্রচলন ঘটার পর ক্রমেই বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বের বেশির ভাগ উন্নত রাষ্ট্র এ ব্যবস্থায় স্বর্ণের মূল্য নির্দিষ্ট করে দেয়। যতদিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ কাগজের মুদ্রার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যেত ততদিন পর্যন্ত টাকার মান নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না।
মুদ্রার মান নিয়ে ঝামেলা শুরু হয় যখন ফিয়াট কারেন্সির আবির্ভাব ঘটে। ফিয়াট মুদ্রাও কাগজের নোটের মাধ্যমে প্রচলিত কিন্তু এই নোটের সাথে বাস্তবের কোনো মূল্যবান স্বর্ণ-রৌপ্য ধাতুর সম্পর্ক নেই। এ ক্ষেত্রে কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের চাহিদামতো ফিয়াট মানি ছাপিয়ে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বর্তমানকালের বেশির ভাগ আধুনিক মুদ্রাই ফিয়াট কারেন্সি। এমনকি বহুল আলোচিত এই আমেরিকান ডলার থেকে শুরু করে বাংলাদেশী টাকাসহ প্রায় সবই ফিয়াট কারেন্সি। তবে পার্থক্য হলো- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ফিয়াট মানি ছাপিয়ে তার নিজের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিয়াট মানি ছাপিয়ে সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে, শাসন করে-শোষণ করে।
উল্লেখ্য, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাজ্য ছিল বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক পরাশক্তি। পুরো পৃথিবীকে লুট করে স্বর্ণের পাহাড় গড়ে নিজ দেশে। তখন লন্ডন ছিল বিশ্বব্যাংকিংয়ের কেন্দ্র এবং সেখানেই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি স্বর্ণ মজুদ। সে কারণে ব্রিটিশ মুদ্রা পাউন্ড স্টার্লিং ছিল সে সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা। ফলে ব্রিটিশ পাউন্ড ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো বিশ্ববাণিজ্যে।
বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় মূলত ইউরোপে। ফলে ব্রিটেনসহ ইউরোপের দেশগুলো যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য তাদের স্বর্ণের মজুদের ভিত্তিতে যে পরিমাণ নোট মুদ্রা ছাপানোর সম্ভব ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছাপিয়েছিল। আস্তে আস্তে যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে নিজেকে জড়ায়নি ঠিক তবে তারা ইউরোপীয় দেশগুলোর কাছে অস্ত্র ও যুদ্ধের রসদ বিক্রি করে মূলত স্বর্ণের বিনিময়ে। ফলে আমেরিকার অর্থনীতি যেমন সমৃদ্ধ হয়, তেমনি বিশ্ব স্বর্ণের উল্লেখযোগ্য অংশ আমেরিকায় জমা হয়।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যুদ্ধে পর্যুদস্ত ব্রিটেনসহ ইউরোপের বেশির ভাগ দেশ তাদের স্বর্ণমান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় মূলত স্বর্ণের ঘাটতি থাকার কারণে। অর্থাৎ তখন তাদের মুদ্রার মান দেশের মজুদকৃত স্বর্ণ মানের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। এ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা চাহিদা ও জোগানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে আর তখন থেকেই ফিয়াট কারেন্সি বা প্রকৃত মূল্যহীন কারেন্সি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে।
ইউরোপে ব্যাপকভাবে ফিয়াট মানিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু হলেও মার্কিন ডলার তখনো ফিয়াট কারেন্সিতে পরিণত হয়নি। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত আমেরিকান ডলার স্বর্ণমান বা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি ধরে রাখে। যেসব দেশ ফিয়াট মানির প্রচলন করেছিল তারা তাদের স্বর্ণের মজুদ বৃদ্ধি করেও মুদ্রার প্রকৃত মান ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। অন্য দিকে, আমেরিকান ডলার স্বর্ণমান বা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ধরে রাখায় ডলার আস্থা অর্জন করে। ধীরে ধীরে আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক দেশ হয়ে উঠে এবং মার্কিন ব্যাংকিং ব্যবস্থা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পাউন্ডের পরিবর্তে মার্কিন ডলার অগ্রাধিকার পেতে থাকে। মার্কিন ডলারকে অধিক নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন দেশ তাদের রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবেও ডলার সঞ্চয় করতে থাকে। একপর্যায়ে অধিক ব্যবহারের ফলে মার্কিন ডলার গ্লোবাল কারেন্সি বা বৈশ্বিক মুদ্রা হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বর্ণের মজুদ বৃদ্ধি করতে শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র তখন তাদের রফতানি করার জিনিসপত্রের বিনিময়ে স্বর্ণ ছাড়া অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণের মজুদ বাড়তে থাকে, বিপরীতে অন্য রাষ্ট্রগুলোর স্বর্ণের মজুদ কমতে থাকে।
বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখনো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রথম আড়াই বছর যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং যুদ্ধরত দেশগুলোর কাছে প্রচুর সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করে। ওই সময়ও যুক্তরাষ্ট্র তার রফতানিকৃত পণ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ছাড়া অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করেনি। এই নীতির কারণে তাদের স্বর্ণ মজুদ ফুলেফেঁপে ওঠে। এমনকি ১৯৪৭ সালে বিশ্বের মোট মজুদকৃত স্বর্ণের শতকরা ৭০ ভাগই ছিল আমেরিকার হাতে। বলতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমেরিকার জন্য এক ধরনের আশীর্বাদ হয়ে আসে। এই বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীতে আমেরিকার অবস্থান চিরদিনের মতো বদলে দেয়। অন্য দিকে ব্রিটেন, জার্মানি ও ফ্রান্সের মতো পরাশক্তিগুলো যুদ্ধে যেমন অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে যায় তেমনি তাদের উপার্জনের প্রধান উৎস, উপনিবেশগুলো একে একে স্বাধীন হয়ে যায়। তখন কেবল আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়।
বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই অন্যান্য রাষ্ট্র অনুধাবন করতে পেরেছিল যুদ্ধপরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র একচ্ছত্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে। যুদ্ধপরবর্তী অর্থনীতি যাতে স্থিতিশীল থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ১৯৪৪ সালে মিত্রপক্ষের ৪৪টি সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ব্রেটন উডস নামক অবকাশযাপন কেন্দ্রে আলোচনার জন্য সমবেত হন। দেশগুলোর প্রতিনিধিরা একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন যা ব্রেটন উডস নামে পরিচিত। এই চুক্তি বিশ্ব অর্থনীতির মেরুদণ্ডে পরিণত হয়। ব্রেটন উডস চুক্তির মাধ্যমেই স্বর্ণকে পাশ কাটিয়ে মার্কিন ডলারকে আনুষ্ঠানিকভাবে রিজার্ভ কারেন্সি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ সময় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মার্কিন ডলারের সাথে স্বর্ণের যে সংযোগ ছিল সেটি বজায় থাকবে এবং আগের মতোই বিনাবাধায় মার্কিন ডলার ইচ্ছামতো স্বর্ণে রূপান্তর করা যাবে। ব্রেটন উডস চুক্তির ফসল হিসেবেই বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক সংস্থা দু’টি বিশ্বব্যাপী আমেরিকার প্রভাববলয় সৃষ্টি করতে প্রধান ভ‚মিকা পালন করে।
বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো এবং জাপান বিশ্বযুদ্ধের দুর্দশা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলে তারা তাদের মজুদকৃত মার্কিন ডলারের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আবারো স্বর্ণ কিনতে শুরু করে, ফলে মার্কিন স্বর্ণযুগ ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। সে সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধের পেছনেও আমেরিকার অনেক টাকা খরচ হয়। সেই সাথে ১৯৬৫ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন গ্রেড সোসাইটি নামে এক বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেন যার উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার শিক্ষা, নাগরিক অধিকার, স্বাস্থ্য খাত ও অনুন্নত অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন করা। ওই প্রকল্পের ব্যয় মেটানোর জন্য মার্কিন সরকার বিপুল ডলার ছাপাতে শুরু করে, ফলে মার্কিন ডলারের সাথে স্বর্ণের সামঞ্জস্য রাখা আর সম্ভব হয়নি।
১৯৭১ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন বিশ্ব অর্থনীতিকে এক বিশাল ধাক্কা দেন যেটি ‘নিক্সন-শক’ নামে পরিচিত। তিনি ঘোষণা করেন, এখন থেকে আর মার্কিন ডলারের সাথে স্বর্ণের কোনো সংযোগ নেই। অর্থাৎ, এখন থেকে কোনো দেশ চাইলেই নির্দিষ্ট মূল্যে মার্কিন ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ কিনতে পারবে না। তার মানে মার্কিন ডলারও তখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুদ্রাগুলোর মতো ফিয়াট কারেন্সিতে পরিণত হয়। রিচার্ড নিক্সন বিশ্বজুড়ে আমেরিকান ডলারের কর্তৃত্ব ধরে রাখতে ও চাহিদা বাড়ানোর জন্য ১৯৭৪ সালে সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মধ্যে একটি চুক্তি হয় যে, পেট্রল কেবল ডলারের বিনিময়ে ক্রয় করতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণকারী একক মুদ্রা হিসেবে ডলারকে প্রতিষ্ঠিত করার ও টিকিয়ে রাখার মহৌষধ ছিল ডলারকে পেট্রোডলারে রূপ দিতে পারা।
প্রশ্ন হলো, মার্কিন ডলার যখন ফিয়াট কারেন্সিতে পরিণত হয় তখন অন্য দেশগুলো কেন মার্কিন ডলারকে ত্যাগ করল না? কেনই বা এখন পর্যন্ত ডলারকে আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে মেনে নিচ্ছে? আসলে মার্কিন ডলারকে ত্যাগ করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হলে নতুন একটি রিজার্ভ মুদ্রা প্রয়োজন হতো। কিন্তু নিক্সন-শক কার্যকর হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠল বিশ্বের প্রধান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাশক্তি এবং এই পরাশক্তির প্রভাবের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করার মতো অন্য কোনো দেশ ছিল না। মার্কিন ডলারের মানের পতন ঘটলেও তাদের আধিপত্য কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি। তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিদ্ব›দ্বী দেশগুলোর বিরুদ্ধে ডলারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।
বিভিন্ন সময়ে ইরান, চীন, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়ার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র মূলত ডলার রক্ষার স্বার্থেই। এর ফলে দেশগুলোর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করা অনেক কঠিন হয়েছে। ইরাক, লিবিয়ার মতো অর্থনীতিতে সমৃদ্ধিশালী দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধুই ডলার না থাকায় বিশ্বের বহু দেশকে দেউলিয়াত্ব বরণ করতে হয়েছে। সদ্য দেউলিয়া হওয়া শ্রীলঙ্কা, লেবানন তার উদাহরণ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বাধার অনেক কারণের কথা বলা হলেও রাশিয়ার ডলার থেকে বের হয়ে আসার প্রচেষ্টা তার অন্যতম।
এক কথায়, সারা বিশ্ব শোষিত হচ্ছে আমেরিকান ডলারে। ফলে ডলারের বিকল্প খুঁজছে সারা বিশ্ব; কখনো ইউরো, কখনো রুবল এবং কখনোবা ইউয়ান। কিন্তু ভয় হলো, সেখানে ওয়াশিংটনের জায়গায় আধিপত্য করবে বেইজিং, মস্কো ও নয়াদিল্লি। সুতরাং কেবল ডলার উচ্ছেদ করে বিকল্প কোনো মুদ্রার আধিপত্য সৃষ্টি না করে এমন মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে যেন প্রতিটি স্বাধীন দেশ স্বাধীনভাবে তার অর্থনীতি ও মুদ্রানীতি পরিচালনা করতে পারে; শোষিত না হয়। প্রশ্ন হলো- সেই ব্যবস্থাটি কী?
ক্রিপ্টোকারেন্সি কি ডলারের বিকল্প হতে পারে?
মুদ্রাবাজারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য বন্ধ করতে অনেকেই ক্রিপ্টোকারেন্সিকে বৈশ্বিক মুদ্রা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করছেন। ক্রিপ্টোকারেন্সি একধরনের ডিজিটাল মুদ্রা যা কোনো দেশ বা দেশের সরকার নিয়ন্ত্রণ করে না; বরং ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বনিয়ন্ত্রিত। ক্রেডিট কার্ডের ধারণা থেকে মূলত ক্রিপ্টোকারেন্সির উদ্ভব।
বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে একধরনের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ডিজিটাল মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় এবং পরের দশকে এই কার্ড অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এরপর অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ডিজিটালি অর্থ আদান-প্রদান শুরু হয়। তবে এ ব্যবস্থার অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে সামগ্রিক অর্থনীতি কিছু লোকের হাতে জিম্মি থাকে। এ ছাড়া লেনদেনের ক্ষেত্রে অর্থের মালিক গোপন তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য হয় এবং নানান ধরনের বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আটকে পড়ে। অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়টি আরো ঝুঁকিপূর্ণ। কম্পিউটারভিত্তিক যোগাযোগের ব্যাপক প্রচলন হওয়ার পর থেকে মানুষ এমন এক ধরনের মুদ্রার স্বপ্ন দেখে আসছে যা কোনো ধরনের তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই পরিচালিত হবে।
সর্বপ্রথম ডেভিড জম ১৯৮৩ সালে ক্রিপ্টোগ্রাফিক পদ্ধতিতে অর্থ আদান-প্রদানের ধারণার প্রবর্তন করেন এবং ১৯৯৫ সালে ক্রিপ্টোগ্রাফিক ইলেকট্রনিক পেমেন্টের প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করেন। তবে তখনো ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা ও নিরাপদ লেনদেন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর প্রযুক্তির অভাব ছিল। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে সাতোশি নাকামোতো নামে এক ছদ্মবেশী চরিত্র এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হন। তিনি ক্রিপ্টোকারেন্সির জনক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এই সাতোশি নাকামোতো আসলে কে, তা কেউ জানে না। এমনকি সাতোশি নাকামোতো নিজেও চান না কেউ তাকে খুঁজে বের করতে পারুন।
কারণ ক্রিপ্টোকারেন্সি মূল ধারণাই হলো- যে কেউ তার পরিচয় গোপন করে নিরাপদে সাধারণ মুদ্রার মতোই এই ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহার করতে পারবে। উল্লেখ্য, ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট খুলতে ব্যবহারকারীর নাম ঠিকানা বা ব্যক্তিগত তথ্যের দরকার হয় না; বরং সরাসরি এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির ওয়ালেটে ট্রান্সফার হয়, মাঝখানে কোনো প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অধিকন্তু, ক্রিপ্টোকারেন্সির সেবা দিতে যেহেতু কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই, তাই কোনো বাড়তি চার্জ নেই।
ক্রিপ্টোকারেন্সি পদ্ধতির প্রথম মুদ্রা বিটকয়েনের সফলতা এবং জনপ্রিয়তা দেখে এরকম অসংখ্য ক্রিপ্টোকারেন্সি উদ্ভব হয়েছে; বর্তমানে এর সংখ্যা চার হাজারেরও বেশি। এর মধ্যে ইথালিয়াম, লাইটকয়েন, রিবল, বাইটকয়েন, গজকয়েন, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।
ক্রিপ্টোকারেন্সির মূল ভিত্তি হলো ব্লকচেইন যা তথ্য সংরক্ষণের এক নতুন পদ্ধতি। ব্লকচেইন এক ধরনের হিসাবের খাতা যা ব্যাংকের মতো ডিজিটাল অর্থনৈতিক লেনদেনের তথ্য সংরক্ষণ করে। তবে এই লেনদেনের হিসাব কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে কুক্ষিগত থাকে না; বরং এই লেজার ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে দেখা যায় এবং প্রতিটি লেনদেন ঘটার সাথে সাথে এই হিসাবের খাতা আপডেট হয়ে যায়। এ কাজ করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, তবে একদল লোক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে। বিনিময়ে ব্লকচেইন সিস্টেম ওই ভলান্টিয়ারদের ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রদান করে; এই প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল অর্থ উপার্জনকে বলা হয় মাইনিং। শক্তিশালী কম্পিউটারের প্রয়োজন হয় মাইনিং করার জন্য।
ক্রিপ্টোকারেন্সির গোপনীয়তা রক্ষা করতে গিয়ে কিছু ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে; যেমন- এর পাসওয়ার্ড একবার ভুলে গেলে অর্থ আর কখনোই ফিরে পাওয়া যায় না, কারণ এখানে পাসওয়ার্ড রিসেটের কোনো সুযোগ নেই। এ ছাড়াও কম্পিউটার ক্রাশ হলেও ক্রিপ্টোকারেন্সি ফিরে পাওয়া যায় না। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, ২০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের বিটকয়েন হারিয়ে গেছে এ কারণে। সাধারণ মানুষের পক্ষে বিটকয়েনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বেশ কঠিন। তবে এই ক্ষতি মোকাবেলার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি রাখার জন্য একধরনের থার্ড পার্টি ওয়ালেটের আশ্রয় নেয়া যায় যাদেরকে ক্রিপ্টো ব্যাংক বলা হয়। যদিও ওয়ালেটগুলো ব্যাংকের মতো নয়; বরং মানি এক্সচেঞ্জের মতো কাজ করে। এসব ওয়ালেট ব্যবহার করে সাধারণ মানিকে ক্রিপ্টোমানি ও ক্রিপ্টোমানিকে সাধারণ মানিতে পরিণত করা যায়। ঠিকমতো ব্যবস্থাপনা করতে না পারলে হ্যাকিংয়ের ঝুঁকিও রয়েছে এই ক্রিপ্টোকারেন্সি কোম্পানির। তবে ধীরে ধীরে সমস্যা থেকে উত্তরণ করে হয়তো এই সীমাবদ্ধতা কমে আসবে।
উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রিপ্টোকারেন্সি হতে পারে কোনো দেশের সরকার অথবা এক দেশে অন্য দেশের অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে একটি নিয়ন্ত্রণহীন অর্থব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য ডলার, রুবল অথবা ইউরোর দরকার হবে না। ফলে কোনো পরাশক্তি কোনো দেশকে শাসন বা শোষণ করতে পারবে না। তবে ক্রিপ্টোকারেন্সির এই নিয়ন্ত্রণহীন অর্থব্যবস্থাই দেশের সুবিধাবাদী স্বৈরসরকার এবং ডলারের মালিকদের জন্য সমস্যার কারণ। ফলে বিশ্বের অনেক দেশেই এ ধরনের মুদ্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবুও ক্রিপ্টোকারেন্সি বিশ্বে এক ধরনের বিপ্লবের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে অনেক জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লেনদেন সমর্থন করছে। তরুণ প্রজন্ম এই নতুন ধরনের মুদ্রা ব্যবস্থাকে খুবই পছন্দ করছে এবং ব্যবহার করছে। সুতরাং ক্রিপ্টোকারেন্সি হতে পারে ডলারের শোষণ ও শাসনের হাত থেকে বিশ্ব অর্থনীতি ব্যবস্থা বাঁচানোর অন্যতম বিকল্প।
লেখক : অর্থনীতিবিদ ও গবেষক