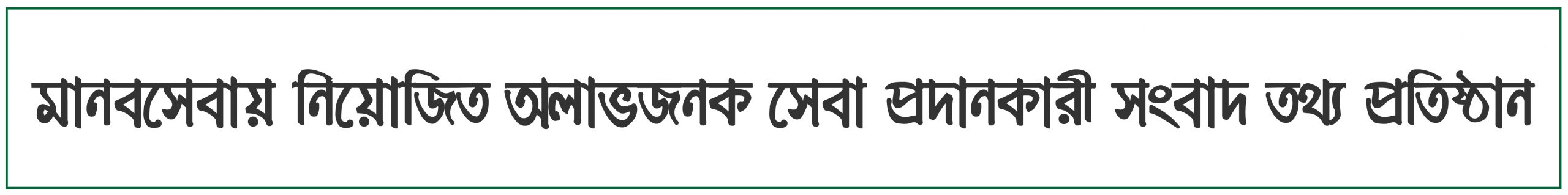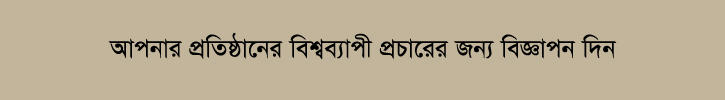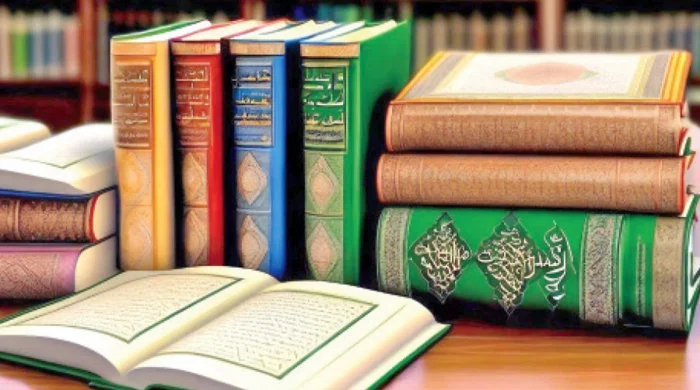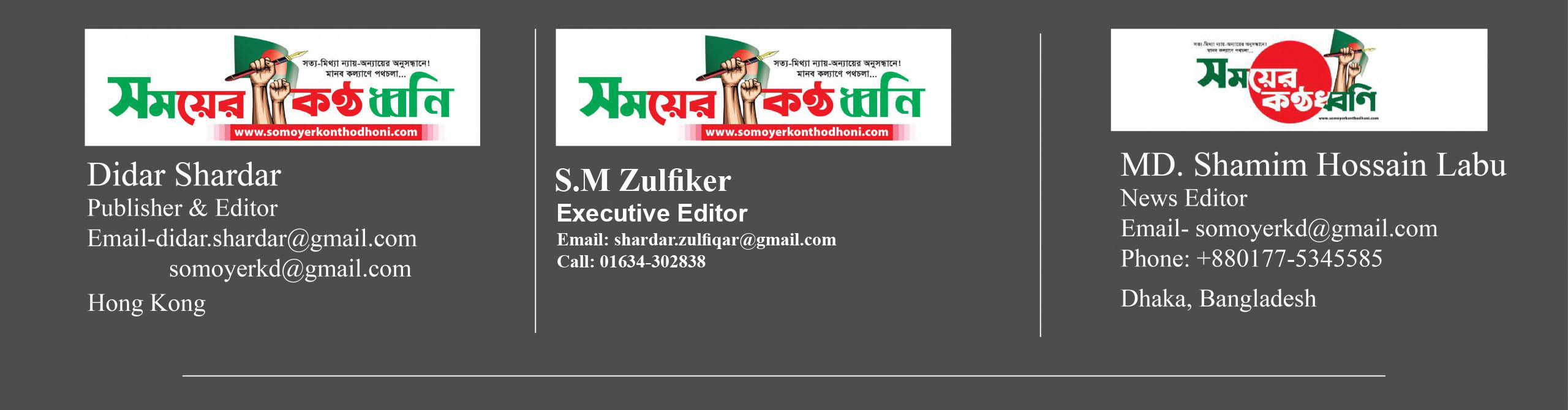ফাল্গুন আসছে, আমরা কেন দ্বিগুণ হতে পারলাম না
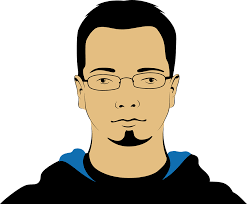
- আপডেট টাইম : রবিবার, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
- ৫ বার পঠিত

গত বছরের ২ আগস্ট ঢাকায় প্রেসক্লাবের সামনে শুরু হওয়া ‘দ্রোহযাত্রা’র কাহিনি এখনো হয়তো অনেকের মনে আছে। সেই মিছিলে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই রিকশাচালক সুজন মিয়ার কথা ভুলে যাননি। দোয়েল চত্বরে দাঁড়িয়ে যিনি মিছিলের সবাইকে অভিবাদন জানাচ্ছিলেন। সুজন মিয়ার স্যালুটের ছবি অভ্যুত্থানের জনৈক্যের অন্যতম প্রতীকী স্মারক। অসংখ্য প্রকাশনার প্রচ্ছদ এখন সেটা। এলাকাবাসী তাঁকে ‘স্যালুট-সুজন’ বলে ডাকে এখন।
২ আগস্ট দ্রোহযাত্রায় অংশ নেওয়া অনেকের নিশ্চয়ই এটাও মনে আছে, দোয়েল চত্বরে সুজন মিয়ার সঙ্গে সেদিন আরও অনেক রিকশাচালক ছিলেন। পায়ে চপ্পল, গায়ে গেঞ্জি আর চোয়াল শক্ত করে রিকশার সিটে উঠে দাঁড়িয়ে থাকা এই মানুষগুলোর কথা মনে পড়ল সম্প্রতি সরকারের ভ্যাটবিষয়ক ঘোষণা দেখে।
কিছুদিন আগে নতুন করে বিবিধ শুল্ক–করের যে ফর্দ জারি হলো, তাতে ১৫০ টাকার নিচের দামের চপ্পলের ওপরও উৎপাদন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ ভ্যাট বসেছে। বলা বাহুল্য, এই কর চপ্পল কোম্পানির মালিকেরা দেবেন না, দেশের উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তরাও খুব বেশি নয়। মূলত সুজন মিয়াদের শ্রেণি অতি কম দামি হাওয়াই চপ্পলের ভোক্তা।
জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের সুজন মিয়াদের মতো এক শর বেশি শ্রমজীবী জীবন দিয়েছিলেন। নতুন করের কোপ যে তাঁদের ওপরও পড়ল, তাতে চলতি সরকারের রাজস্বনীতির অগ্রাধিকার খানিকটা বোঝা গেল।
ছয় মাসের রাজনৈতিক অডিট দরকার
যে দেশের রাজধানীতে ২০ কোটি টাকা দামের ৭ হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাটও তৈরির আগে বিক্রি হয়ে যায়, যেখানে জনসংখ্যার ওপরের দিকের ১০ শতাংশের হাতে জাতীয় আয়ের ৪১ শতাংশ থাকে এবং নিচের দিকের ১০ শতাংশের হাতে থাকে ওই আয়ের মাত্র ১ দশমিক ৩ শতাংশ, সেখানে করারোপের অগ্রাধিকার দিয়ে অবশ্যই সে দেশের সরকারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ভালোবাসার ধরন বোঝা যায়। ১৫০ টাকা দামের হাওয়াই চপ্পলের ওপর ভ্যাট আরোপ অর্থনীতির বিচারে ছোট ঘটনা হলেও রাজনৈতিক দর্শনের দিক থেকে সমকালীন সরকারকে বোঝার বেশ বড় উপাদান।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কেউ না কেউ প্রতিদিন জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের অঙ্গীকার ও চেতনার কথা বলছেন। প্রচারমাধ্যম থেকে সেগুলো সবাইকে নিয়মিত শুনতে হয়। এ রকম শোনার প্রায় ১৮০ দিন হলো। অর্থাৎ প্রায় ছয় মাস গেল ‘লাল জুলাইয়ে’র। এখন নিশ্চয়ই এই সরকারের কথা ও কাজের একটা অডিট বা হিসাব–নিকাশ হতে পারে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতেই সেটা হওয়া দরকার।
আশার সূচকগুলো যখন পড়তির দিকে
একাত্তর ও নব্বইয়ের পাশাপাশি চব্বিশের অভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বড় অর্জন। কিন্তু সুজন মিয়ারা কী পেলেন এই অভ্যুত্থান–পরবর্তী ছয় মাসে?
আমরা দেখেছি, শহীদেরা ‘৩৬ জুলাইয়ে’র আগে নানা আদর্শের মানুষদের এককাতারে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। বিরল এক সফলতা ছিল সেটা। অথচ ছয় মাস পেরোতে না পেরোতেই এখন দেশজুড়ে প্রবল রাজনৈতিক বিভক্তি। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতিপক্ষ বা খলনায়ক হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা দেখা যাচ্ছে।
কথা ছিল, আসছে ফাল্গুনে ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থানের শক্তি দ্বিগুণ হবে। অথচ ইতিমধ্যে বিভিন্ন পেশাজীবীরা দাবিদাওয়া তুলে ধরতে গিয়ে পুলিশি লাঠিপেটার শিকার হচ্ছেন। ঢাকার কেন্দ্রস্থলে পাহাড়িদের রক্তাক্ত হতে দেখা গেল। জেলা-উপজেলায় মাজার-দরবার শরিফগুলো একের পর এক গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে মেয়েরা ফুটবল-ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে অসামান্য অর্জন নিয়ে এসেছে, তাদের খেলাধুলার আয়োজনে সহিংস বাধা তৈরি হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে এতিম হয়ে ঘুরছেন সাভার-আশুলিয়া-গাজীপুরজুড়ে প্রায় ৬০টি কারখানার কাজ হারানো শ্রমিকেরা। মুদ্রাস্ফীতি চলছে ডবল ডিজিট হারে। মার্কেট-সিন্ডিকেটগুলো বহাল তবিয়তে আছে।
২৯ জানুয়ারি সিপিডির গবেষকেরা দেশবাসীকে জানালেন, গত ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববাজারে প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দর যেখানে ছিল ১২৮ টাকা, দেশের বাজারে সেটা ১৬৮ টাকায় কিনতে বাধ্য হয়েছেন ক্রেতারা। কৃষকেরা যে চালের দাম পান কেজিতে ৩৩ টাকা, খুচরা ক্রেতা সেটা কিনতে বাধ্য হচ্ছেন গড়ে ৬৫ টাকায়।
অথচ গণ-অভ্যুত্থানের সরকারের কাছে বাজার–মাফিয়াদের গুঁড়িয়ে দেওয়ার দাবি ছিল। এই সরকারের পেছনে এত বিপুল জাতীয় সমর্থন ছিল যে এসব খাতে পদক্ষেপ নেওয়া কঠিন হতো না। কিন্তু সেসব হয়নি। তবে অভ্যুত্থানের সমর্থনে এবং তার কাছে প্রত্যাশা জানিয়ে সভা-সেমিনার এখনো চলছে। নাগরিক বুদ্ধিজীবী আর এনজিও ব্যক্তিত্বরা বিভিন্ন কমিশনের প্রতিবেদন দেখিয়ে ফটোসেশন করছেন প্রায় দিন।
প্রশ্ন হলো, এসব সভা-সেমিনার-কমিশনের সুপারিশ কারা বাস্তবায়ন করবেন? রাজনৈতিক দল ও নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সম্মতি ও অনুমোদন ছাড়া কি জনগণ আদৌ এসব সুপারিশের সুফল পাবেন? উত্তরটা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানেই বোঝা যায়। তাহলে মাঠে-ময়দানে রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতিপক্ষ বানানো হচ্ছে কেন? রাজনীতিবিদদের সঙ্গে না নিয়ে অনির্বাচিত সরকার কি আদৌ অর্থবহ কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম?
পদ্ধতিগতভাবে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া মানুষগুলো চিহ্নিত হলো না
হয়তো এটা ভালো হতো যদি পুরো সরকার অভ্যুত্থানকারীদের হতো এবং সরকার নিজেই তার করা কমিশনগুলোর সুপারিশ বাস্তবায়ন করত। কিন্তু তা হয়নি, যদিও এই উপদেষ্টা পরিষদ পুরোই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পছন্দে হয়েছে। অন্তত ৬ আগস্টের ঘটনাবলি তা–ই সাক্ষ্য দেয়। গত ছয় মাসে সেই সরকারের সামর্থ্য ও দক্ষতা অনেকখানি স্পষ্ট। এটাও বোঝা গেল, প্রশাসনের সব অংশ সরকারকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করছে না। আবার যেহেতু রাজনৈতিক ঐক্যের জায়গাটাও ভেঙে গেছে এবং প্রতিদিন তীব্র বাগ্যুদ্ধ দেখা যাচ্ছে, সুতরাং অনির্বাচিত এ সরকারের পক্ষে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সংস্কার সম্ভব কি না, তা নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য সংশয় আছে।
রাজধানীর মতিঝিল আর রমনা পরিসর ছেড়ে সরকার শারীরিকভাবে খুব একটা জেলাগুলোতে যাওয়ার সময় পেল না গত ছয় মাসে। সংগত কারণে মাঠ প্রশাসনে ঢিলেঢালা ভাব এসেছে। রুটিন কাজের বাইরে নতুন উদ্যম নেই সেখানে। তাতে আইনশৃঙ্খলার বর্তমান অবস্থার জন্য দেশের জনগণকেই বরং ধন্যবাদ দিতে হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীরাও এ রকম ধন্যবাদের কিছুটা ভাগ পেতে পারেন।
ক্রুদ্ধ প্রতিশোধে মেতে ওঠেননি তাঁরা। কিন্তু তাঁদের প্রতিনিয়ত গালিগালাজ আর দোষারোপে রাখলে প্রশাসনের বিষণ্ন অংশ সেই বিভাজনের সুযোগ নেবে এবং নিচ্ছেও। সুজন মিয়ারা কোপের শিকার হলেও সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার কথা শোনা গেছে। রক্তের দাগ শুকানোর আগেই গণ-অভ্যুত্থানের সুফল যেন ভিন্ন শ্রেণিগোষ্ঠীর রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছে। ন্যায্যমূল্যের শহুরে ট্রাক সেলও কমে গেছে।
আইএমএফের প্রেসক্রিপশন যদি কেবল সুজন মিয়াদের পকেট খামচে ধরার জন্য হয়, তাহলে বিএনপি-জামায়াত-আওয়ামী লীগের আমলের চেয়ে এই আমল কীভাবে পৃথক? বিগত দুটি জাতীয় নির্বাচনে সহযোগী ভূমিকায় থাকা প্রশাসনিক মানুষগুলোর দিক থেকে জনগণ কোনো জবাবদিহি পায়নি আজও। পদ্ধতিগতভাবে ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার রাষ্ট্রীয় কাঠামোটা স্পষ্ট হওয়া জরুরি ছিল।
অথচ ভাদ্র থেকে মাঘ পর্যন্ত কেবল এটাই শোনা যাচ্ছে, সংস্কারের জন্য অনেক অনেক সময় দরকার। সরকার বারবার সময় চাইছে। কিন্তু কিছু সংস্কার নিশ্চয়ই পেরিয়ে আসা ছয় মাসে করা যেত। এ সময়ে কি শ্রম আইন ও ভূমি আইন যুগোপযোগী করা যেত না? মজুরি বোর্ড বা লেবার কোর্টকে সংস্কার করলে রাজনীতিবিদেরা বাধা দিতেন কি? দেশে প্রায় সাত কোটি শ্রমজীবী এখন। এ রকম সংস্কারগুলো করে নিচুতলায় বিস্তর স্বস্তি আনা যেত। অন্তত ‘চার বছর তত্ত্বে’র খানিকটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হতো তাতে।

চাওয়া এখন ন্যূনতম কিছু
ছয় মাস কম সময় নয়। এর মধ্যে স্থানীয় সরকার থেকে শুরু করে বিদেশনীতি ও বিদেশি বিনিয়োগ পর্যন্ত অনেক বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে কাছে টেনে জাতীয় ঐকমত্য তৈরি করে বেশ কিছু দিকনির্দেশনা দেওয়া যেত এর মধ্যে। রাজনৈতিক দলগুলোকে সরকারের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত দেখলে সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন এখনকার মতো উদাসীনতা দেখাতে পারত না। চারদিকে শুরু হওয়া নানা খাতের ধর্মঘটের নৈরাজ্যও তখন সামাল দেওয়া সহজ হতো।
প্রশ্ন তোলা যেত, বিগত সময়ের দুর্নীতিবাজেরা কীভাবে অবলীলায় পালিয়ে যেতে পারলেন? কারা তাঁদের সেই সুযোগ করে দিলেন? মনে হয় না, এসব প্রশ্ন তোলার হিম্মত সরকারের কারও আছে। থাকলে এত দিনে নিশ্চয়ই সেটা উঠত।
উল্টো জোর দেওয়া হলো ‘সাংস্কৃতিক যুদ্ধে’র ওপর। ক্যাম্পাসগুলোতে গ্যাং কালচার আর ক্যাম্পাসের বাইরে মব কালচার ভীতির পরিবেশ তৈরি করল চারদিকে। রাতারাতি রাষ্ট্রীয় নানা সিদ্ধান্ত পাল্টে যাচ্ছে ‘মবে’র চাপে। পাঠ্যপুস্তক ও বাংলা একাডেমির পুরস্কারের বেলায় মোটাদাগেই সেটা দেখা গেল। কাউকে পুরস্কার বা পদক দিয়ে ‘মবে’র চাপে সেটা কেড়ে নিয়ে পরিবার ও সমাজে ওই মানুষদের হেনস্তা করার সংস্কৃতি নজির হিসেবে খুব খারাপ। এতে সমাজে বারবার এ প্রশ্নই তৈরি হচ্ছে, সরকার কি কিছু গোষ্ঠীর হাতে জিম্মি?
যে তরুণেরা দারুণ অগ্রসর এক রাজনৈতিক চৈতন্য নিয়ে ৩৬ জুলাইয়ের জন্ম দিয়ে শহীদ হয়ে গেলেন, তাঁদের জীবিত সহযোগী একাংশকে ছয় মাস ধরে হুমকির সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত হতে দেখলাম আমরা। এর মধ্যে অনেকে বেশ জোরের সঙ্গে একাত্তর, ১৬ ডিসেম্বর, জাতীয় পতাকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাতে থাকলেন। খুব সচেতনভাবে যেন লীগ শাসনামলের সঙ্গে একাত্তরকে মিশিয়ে দিয়ে তরুণদের আক্রোশের সামনে ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে।
একাত্তর ও চব্বিশকে বিপরীত মেরুতে দাঁড় করানোর সচেতন প্রচেষ্টাও লুকাচ্ছেন না অনেকে। সব মিলে গত ছয় মাসে ঝুঁকিতে পড়তে শুরু করল বাংলাদেশের এত দিনকার অনেক রাজনৈতিক অর্জন ও সামাজিক ঐতিহ্য। সবচেয়ে হতাশার দিক, যে শিক্ষার্থীরা ছয় মাস আগে সবার নায়কের আসনে ছিল, এখন তাদের সঙ্গে মূল সমাজের বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে ধীরলয়ে। এটা আবার পুরোনো আমলের পালিয়ে যাওয়া শক্তিকে ধীরে ধীরে অক্সিজেন জোগাচ্ছে। চলতি আবহকে তারা অতীত অনাচার আড়াল করতে কাজে লাগাতে চাইছে।
এ রকম এক অবস্থায় এসে হাটে-মাঠে-ঘাটে মানুষের চাওয়া ন্যূনতম জায়গায় চলে গেছে। আগস্টের বড় কল্পনা এখন আর নেই। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সংস্কার হোক বা না হোক, অন্তত সামাজিক স্থিতিশীলতা যেন থাকে, সেটাই তাদের আপাতচাওয়া।
আমজনতা দুঃখে পড়েই এখন নির্বাচিত সরকার চায়, যে সরকারের মন্ত্রীরা অন্তত শহরে ফটোসেশনের পাশাপাশি ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যন্ত যাবেন। নির্বাচনে জনসমর্থিত দল যদি রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার না–ই করে, তবু সেই বাস্তবতা আমাদের মেনে নিতে হবে। কারণ, জনগণের সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছাড়া সংস্কারের স্বপ্ন দেখে বা দেখিয়ে বাস্তবে এগোনো যাবে না। মাঠে-ময়দানের দীর্ঘ এক রাজনৈতিক কাজ সেটা।
যে শিক্ষার্থীরা সংস্কার প্রশ্নে এখনো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁরা সেই কাজ করতে পারেন এবং সে জন্য তাঁদের সরকারের চৌহদ্দি পুরোপুরি ত্যাগ করে রাজনীতি ও নির্বাচনে শামিল হওয়াই উত্তম হবে, সেটা গণপরিষদ নির্বাচন বা সাধারণ নির্বাচন, যা–ই হোক। তবে ‘কিংস পার্টি’–জাতীয় কিছু হলে বিভেদ ও সংঘাত অনেক বাড়বে, যার স্পষ্ট লক্ষণ আছে। প্রত্যাশিত ‘ফাল্গুনে’র কফিনে শেষ পেরেক হবে সেটা।
- আলতাফ পারভেজ গবেষক